রবীন্দ্র ভাবাদর্শে রবীন্দ্র ভাবনৃত্য
চন্দ্রাবলী ঘােষাল
গবেষক, সঙ্গীত ভবন, রবীন্দ্র সঙ্গীত নৃত্যনাট্য বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
/images.anandabazar.com/polopoly_fs/1.29491.1399675005!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_390/image.jpg)
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বড় হয়ে উঠেছেন এমন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের মধ্যে আশ্রম কন্যা অমিতা সেন অন্যতম। তার আশ্রম জীবনের স্মৃতিকথা শান্তিনিকেতনে আশ্রম কন্যা গ্রন্থে তিনি সরাসরি উল্লেখ করেছেন তার নৃত্য সম্বন্ধে নিজস্ব গভীর অনুভূতির কথা। তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে তার অনুভূতির কথা। তিনি বলেছেন “ভাব নৃত্য রবীন্দ্রনাথের অভিনব মর্মস্পর্শী এক সৃজন। মনের ভাবটি যেমন তিনি তার গানের সুরে বইয়ে দিলেন, তেমনি তার হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা ফুটিয়ে তুললেন নৃত্যের ছন্দে। আমাদের দেশে সংকীর্তন নৃত্যে, বাউল নৃত্যে প্রেম ও ভক্তির বন্যা বয়ে চলেছে বহুকাল ধরে। সেই ধারায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরের রসলীলা রূপ পেল তার ছন্দে। তার নৃত্যদোলায় ঝরে পড়ে বর্ষার ধারা, বসন্তে ফুটে ওঠে পুষ্পকলি, নব কিশলয়ে লাগে হিল্লোল, শুকনােপাতা ছড়িয়ে পড়ে, কোন দূরে দূরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে আনন্দ, মনের বেদনা ওঠে বেজে। অপূর্ব ভাব নৃত্য তার। যাৱা না দেখেছেন তাদের বােঝানোর ক্ষমতা নেই, আমার ভাষা যোগাবে না।”।[১]
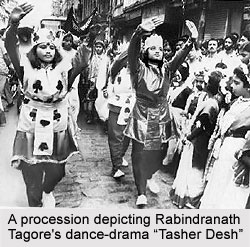
এই ভাব নৃত্য তিনিই শেখাতেন বালিকাদের। মনের আবেগে রচনা করেছেন নতুন নতুন গান, সেই গান ফুটিয়ে তুলেছেন নৃত্যে। সেই নৃত্য মেয়েরা শিখেছে তারই কাছে। মনে পড়ে ঋতুরঙ্গের মহড়া চলেছে। রচনা করলেন, ‘শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে’। পরদিন উদয়নে শেখাচ্ছেন সেই গানের ভাব নৃত্য মেয়েদের ‘কদম ঝরে হায় হায় হায়’ । মুগ্ধ নয়নে আমরা দেখছি তার হাতের ভঙ্গিতে ঝরে পড়ছে ফুল। ‘হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এলে’ শীত ঋতুর এই গানে শেখাচ্ছেন আগুন পােয়ানাের নাচ, ঘুরে ঘুরে হাত দুখানি আগুনের উপর নানা ভঙ্গীতে মেলে ধরেছেন, কখনাে বসে কখনাে দাড়িয়ে। কি অপরূপ আগুন পােহানাের নাচ, এরকম কত কত গানে নৃত্য শিক্ষার ছবি মনে গাঁথা হয়ে আছে।
ক্রমে এল টেকনিকের যুগ, নানা দেশের নাচের টেকনিক শেখানাে শুরু হল রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে এবং ব্যবস্থায়। রবীন্দ্র নৃত্য ক্রমশ আরাে স্বার্থক ভাবে ফুটে উঠল কবির নির্দেশনায়। শিশু যতদিন হাঁটতে না শেখে মায়ের কোলে আশ্রয়টি সে পায়, হাঁটতে শিখলে মায়ের স্নেহ সতর্ক দৃষ্টি তাকে ঘিরে রাখে, কিন্তু মায়ের কোলটি সে হারায়। আমরাও সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যের নিবিড় কোলটির স্পর্শ হারালাম। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় ভাবনায় পরিকল্পনাতেই নৃত্য গড়ে উঠেছে তার শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু গানের প্রথম কলি থেকে শেষ কলি পর্যন্ত নিজে গেয়ে, নিজে নেচে হাত ধরে নাচ শেখানে ক্রমশই তাঁর থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। চরমতম দুঃখের বিনিময়ে নৃত্যের পরমতম উৎকর্ষের বিকাশ হল রবীন্দ্রনাথের সহায়তায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেকাল’ কবিতায় লিখেছেন,
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে—
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বসত সন্ধ্যা হলে,
ক্রীড়াশৈলে আপন-মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি।
জীবনতরী বহে যেত
মন্দাক্রান্তা তালে
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে॥[২]
রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালকে পাননি। আমরা পেলাম বিশ্বকবির কালকে। বিশ্বকবিকে পেলাম তার নবরত্নের মাঝে। পরম সৌভাগ্যের জোরে আমরা পেলাম কবির উজ্জয়িনী- শান্তিনিকেতনের বিজন প্রান্তে কাননঘেরা বাড়ি শিরীষ, বকুল, শেফালিতলে কবির সুকণ্ঠের গান, আবৃত্তি, পাঠ এর ভিতর দিয়ে আমাদের জীবন তরী সেদিন বয়ে চলত মন্দাক্রান্তা ছন্দে।
রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা অপর এক ব্যক্তিত্বময়ী শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী, তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, ”রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই, কারণ তিনি নিজেই সেই বিষয়ে প্রভৃত পরিমানের লিখে গেছেন শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু তার প্রচলিত নৃত্য সম্বন্ধে বলার আছে। শুধু নৃত্য নয়, বেশভূষা, অলংকার, মঞ্চসজ্জা, প্রভৃতি তাঁর সময়ে তার নির্দেশে যা হতাে সে বিষয়ে অবহিত করা দরকার। সমগ্র ভাবেই তার প্রচলিত ধারা মনে রাখা দরকার।”[৩]
রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে যেভাবে নৃত্য হওয়া উচিত অর্থাৎ গানের কথার ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে তা কদাচিৎ দেখা যায়। নাচের টেকনিক গান কে ছাড়িয়ে যায়।
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নাচ তার গানকে মূর্ত করে তুলবে, তার টেকনিক গান কে ছাড়িয়ে যাবে না। তাই তিনি নিজে নাচ পরিচালনা করতেন, গানের সঙ্গে নাচের কম্পােজিশন বুঝিয়ে দিতেন। এই নৃত্য ধারাকে ভাব নৃত্য বলতেন। তখনকার দিনে মণিপুরী নাচ শেখানাে হত, মণিপুরী নাচে সঙ্গে মিলিয়ে ভাব নৃত্য করা হত। পরে যখন কথাকলি, ভরতনাট্যম বেশ ভালাে করেই প্রচলন হলাে তখন গুরুদেব এইসব টেকনিক মিলিয়ে ভাব নৃত্যই করাতেন।
গুরুদেবের অনেক লেখা থেকে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়, তিনি যেমন নানা ধরনের সুরে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক গান রচনা করেছেন, যেমন শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে নেওয়া অনেক গান আছে, কীর্তনাঙ্গ বাউলাঙ্গ গানও আছে, সাবিত্রী গােবিন্দের কর্ণাটকী গানের থেকেও তেমনি কি অপূর্ব সুর সৃষ্টি করে গেছেন, তেমনি নানা দেশে নানা ধরনের নৃত্য শৈলী দেখেও তিনি প্রেরণা পেয়েছেন। তাও তার লেখা থেকে জানা যায়। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য সম্পর্কে কিছু কথা আলােচনা করার প্রয়ােজন আছে। সুদূর অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে মানুষ যেমন স্পন্দিত হল ছন্দে, সেই দিনই তার জীবনে এলাে গতিবেগ। সুচীত হল তার জয়যাত্রা। জীবনকে সহজ ও সাবলীল করে ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ কর্মশক্তির অপব্যয় হয় না। শক্তিকে সংযত, সংহত ও একাগ্র করে তােলাই তার কাজ। বিদ্রোহী মানুষ বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতির সঙ্গে দ্বিমুখী সংগ্রাম করে মনুষ্যত্বকে মহিমান্বিত করার পন্থার সন্ধান পেয়েছে। এই বিশ্ব ছন্দের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনে ভাষা সৃষ্টি হবার আগেই নৃত্য হয়ে উঠেছে মানুষের ভাবের বাহন।
১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে গুরুদেব নৃত্য সম্পর্কে উৎসাহিত বােধ করেন। গুরুদেবের নানান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অনেকটাই জায়গা জুড়ে আছে। সর্বপ্রথম ত্রিপুরায় মণিপুরী নৃত্য শৈলী দর্শনের প্রায় কুড়ি বছর পরে সিলেট ভ্রমণের সময় সেই মণিপুরী নৃত্য শৈলী দর্শনের অভিজ্ঞতা তাকে নৃত্যনাট্য রচনা করার প্রেরণা যােগায়।
গুরুদেব শান্তিনিকেতনে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য ধারার ঐশী মন্ডিত মণিপুরী নৃত্য শৈলীর মাধ্যমে আশ্রম নৃত্য ধারার প্রচলন করেন। মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সংবেদনশীল আবেদনকে। সেই আবেদন তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল।
মণিপুরে প্রাক বৈষ্ণব যুগের যে নৃত্য ধারা দেখা যায় তাও ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনে পরিপূর্ণ। মণিপুরবাসীগণ তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের সুচারু ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে যখন বৈষ্ণব ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা লাভ হল তখনও তদ্দেশীয় ঐতিহ্য অনুসারে নব সংস্কৃতিতেও নৃত্যগীত এক বিশেষ মহিমায় প্রতিষ্টিত হল। বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল ভক্তি এবং পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সেই কারণে প্রথম পর্বের বৈষ্ণবীয় সাধনা প্রধানত ছিল ব্যক্তিগত চেতনা কেন্দ্রিক। চৈতন্য লক্ষ্য করেছিলেন যে ওই ধরনের সাধনা কেন্দ্রিক আচরণ অতিসাধারণ এর পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারণে তিনি আপামর জনসাধারণের মনে ভক্তি এবং প্রেমবােধ কে জাগ্রত করার জন্য নাম জপ ‘নাম কীর্তনকেই বেছে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং নানাভাবে খণ্ডিত জনসমাজকে একত্রিত করে পরস্পরের মধ্যে ভাতৃত্ববোধের জাগরণ ঘটিয়ে মানুষের মনে একটি অখণ্ড ভালােবাসার স্রোত প্রবাহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নগর কীর্তনের সূচনা ঘটান। প্রতি মানুষের মধ্যে কৃষ্ণের অবস্থিতি এই কল্পনায় কীর্তন সংগীতে তিনি যে কৃষ্ণ প্রেম এবং কৃষ্ণ প্রাণ তার জোয়ার এনে দিয়েছিলেন তা একদিকে যেমন আঙ্গিকের বৈচিত্র চমৎকার অনাদিকে তেমনি মানুষের হৃদয় থেকে ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থচেতনা দুইটি অধর্মকে দূর করে দেবার একান্ত সহায়ক। এই নাম কীর্তন এই মৃদঙ্গ এবং করতাল এর ব্যবহার এবং নৃত্যছন্দে পথপরিক্রমা মানুষের সুর ও ছন্দ চেতনাকে জাগ্রত করে এই নব্য রীতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ কে আরাে বাড়িয়ে তােলে। এই চৈতন্যদেবের কীর্তন আঙ্গিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মচারণ যখন মণিপুরে প্রবেশ লাভ করে তখন প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে ভরপুর এই পূর্ব ভারতের কাশ্মীর তাকে বরণ করে নেয়। সুর ও ছন্দ মণিপুরীদের সহজাত স্বভাৰ এর মধ্যে বিরাজমান। প্রকৃতি যেখানে রূপের ভাণ্ডারের দ্বার উন্মােচিত করে মণিপুরকে সমৃদ্ধ করেছে সেখানে তার সন্তান সন্ততি সুর ও সৌন্দর্যের পূজারী হবে সেটাই স্বাভাবিক। কীর্তন আঙ্গিক বৈষ্ণব মতবাদকে সারা মণিপুর সাগ্রহে বরণ করে নেয়।
এই ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত ঐশী ভাবাপন্ন মণিপুরী নৃত্য শৈলী গুরুদেবের মনকে আকর্ষণ করেছিল বারবার। নৃত্যকেই শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এক ভিত্তি তৈরি করেছিলেন এই মণিপুরী নৃত্য শৈলীর মাধ্যমে শান্তিনিকেতন আশ্রমের অঙ্গনে। নৃত্য প্রয়ােগের প্রথম পর্যায় দক্ষ শিল্পীদের অভাব থাকায় গুরুদেব অনেক সময় নিজেই সহজভাবে সংগীতের ভাব প্রকাশের উপযােগী নৃত্য শিক্ষা দিতেন। প্রথমেই মূকাভিনয়, গীতাভিনয় ও দেহ ভঙ্গিতে একটু ছন্দ লাগিয়ে অভিনয় করা হত। একটি বিষয় লক্ষ্য করার যে বিভিন্ন নৃত্য পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হলেও মূল নাট্য প্রচেষ্টার একটি কাব্যধর্মী সুরকেই অনুসরণ করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রথম কিছু খণ্ড খণ্ড নাচের সঙ্গে বিভিন্ন ঋতু সংগীত আনুষ্ঠানিক সংগীতের নৃত্য রূপ দেওয়া হত। পরে গীতিনাট্য এবং নাটকের মধ্যেও খণ্ড খণ্ড নৃত্য সংযােজনা করা হয়েছে।
জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে গুরুদেব বুঝেছিলেন যে নাচের আবেদন মানুষের কাছে অন্যান্য শিল্পকলার থেকে অনেক বেশি। অনেক সহজে সাধারণ মানুষকে অনেক বড় কথা বলা যায়, বড় দর্শন বােঝানাে যায়। প্রতিমা দেবী তার ‘নির্বাণ’ বইতে উল্লেখ করেছেন যে শাপমােচন এর যুগে প্রথম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় হল এই নাটকীয় সংঘাতকে বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তােলার জন্য মুক অভিনয় দ্বারা ভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। [৪]
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা
১৯৩৬ সালের মার্চের মাঝামাঝি গুরুদেব কলকাতায় চিত্রাঙ্গদা অনুষ্ঠান করান। চিত্রাঙ্গদার কবিতাকেই প্রথম দেওয়া হয়। এই কবিতার সাঙ্গীতিক আবেগ নাচের সম্পূর্ণ উপযােগী। কবিতার চিত্রাঙ্গদা যেন সংগীতের মধ্য দিয়ে রেশ পরিবর্তন করেছেন মাত্র তারই শৈর্যের নিছক রূপ জেগে উছেঠে তাল ও সুরের বিচিত্র ছন্দে। এখানে বিষয় গৃহীত হয়েছে পাহাড়ঘেরা সুন্দর মণিপুর রাজ্যের রাজকন্যাকে নিয়ে।
শিবের বরে মণিপুর রাজবংশে কোন পুত্রী জন্মাবে না, এই আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন মণিপুরের রাজা। কিন্তু তথাপি পুত্রী চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয়। রাজা তাকে পুত্ররূপে বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে ওঠে। শৌর্যে-বীর্ষে যেকোনাে বীর্ষবানের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। একদিন ব্রতচারী অর্জুন তার যাত্রাপথে শয়ন করায় সে তাকে সেখান থেকে সরানাের জন্য সখীদের আহ্বান করে। কিন্তু এই বীর্ষবর্তী নারীকে না চিনে অর্জুন তাকে বালক বলে অভিহিত করেন এবং নিজের পরিচয় দেন। চিত্রাঙ্গদা স্তম্ভিত হতচকিত হয়ে পড়ে। কারণ তার চির আকাঙ্খিত বীরপুরুষ তাকে যুদ্ধে আহ্বান না করে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই মনােবেদনা কোথায় রাখবে পুরুষবেশী রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। এতদিনে নারীর স্বভাব সুলভ মুগ্ধতায় বীর্যবান অর্জুনকে স্বামী রূপে কামনা করেছে। কিন্তু নারীর কমনীয় লাবণ্য হীনতায় চিত্রঙ্গদা নিজেকে অর্জুনের মনােহরনের যােগ্য করে তুলতে পারেননি।
চিত্রাঙ্গদা মদন দেবের দয়া প্রার্থী হন এবং এক বছরের জন্য রূপ-লাবণ্য কামনা করেন। মদনের বরে সে রূপলাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন তাকে কামনা করেন। এইখানেই দেহজ রূপ আত্মজ রূপকে পরাভূত করে। বহিরঙ্গের কাছে অন্তরঙ্গতার হার হয়। কিন্তু তবু এটাই সব নয়। প্রেম লীলায় অন্য স্বাদ আছে, আছে ক্লান্তি। গ্রামবাসীদের কাছে তাদের অর্জুন জানতে পারেন তাদের রক্ষাকারী একজন নারী। তিনি চিত্রাঙ্গদা। সে সময় তিনি তীর্থ গেছেন। ঐ বীর রমনীর পরিচয় পাওয়ার জন্য অর্জুনের মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। অবশেষে প্রকৃত প্রেমের উন্মেষ ঘটে। চিত্রাঙ্গদা আসেন সমস্ত মিথ্যার আবরণ ভেদ করে। সত্য উদ্ঘাটিত হয়। বীরাঙ্গনাকে অর্জুন গ্রহন করেন তার সাথী হিসেবে। অবশেষে এখানে প্রেমের জয় হয়। বাইরের রূপ অন্তরের অরূপের কাছে নতি স্বীকার করে।
নৃত্যনাট্য শ্যামা :
‘শ্যামা’ প্রথমে পরিচয় কাব্যনাট্য হিসেবে ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকতনে সেপ্টেম্বরে মঞ্চস্থ হয়। শ্যামা নৃত্যনাট্যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য ও লােকনৃত্যের সমাবেশে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত হয়। এই কাব্যনাটোর বক্তব্যও উচ্চবিত্ত রাজবাড়ীর ঘটনা। রাজ কন্যা শ্যামা কাহিনীর মূল চরিত্র। এক সুপুরুষ বণিকের বেচাকেনা দিয়ে কাহিনী সূচনা। রাজবাড়ীতে রাজমহিষীর গহনা চুরি নিয়ে বজ্রসেন নামক বণিকের সঙ্গে প্রহরীর বিবাদের সূচনা হয়। নৃত্যরতা শ্যামার গৃহাঙ্গন দিয়ে প্রহরীরা যখন মহেন্দ্র নিন্দিত কান্তি বজ্রসেনকে নিয়ে কারাগারের দিকে যায় তখন বজ্রসেনের সৌন্দর্যে শ্যামা মােহিত হয়। সে প্রহরীর কাছে দু’দিনের সময় চেয়ে নেন। এইখানেই উভয়ের মধ্যে প্রেমের সূচনা হয়। কিন্তু শ্যামা উত্তীয় নামক এক কিশােরের প্রেমের বিনিময় অর্থাৎ এই উত্তীয়কে নিজের প্রেমে প্রভাবিত করে তার প্রাণের বিনিময়ে বজসেনের প্রাণ রক্ষা করেন। পাপের বিনিময়ে তিনি প্রেম কে পেতে চান। বজ্রসেন কে কারা মুক্ত করে দুজনে রাজপুরী থেকে পালিয়ে যান।
কিন্তু প্রেম বিধুর দুই প্রাণের মধ্যে বারবার আশা-নিরাশার দোলা লাগে। বারবার বজ্র সেন জানতে চায় কি উপায়ে শ্যামা তাকে মুক্ত করেছে। অনেকবার বিমুখ করেও অবশেষে শ্যামাকে সত্য ঘটনা বলতেই হয়। সত্য উদঘাটিত হলে, সত্যের কাছে প্রেমের পরাজয় ঘটে, বারবার বজ্রসেন শ্যামা কে ধিক্কার দেন। পাপিষ্ঠা বলে তাকে পদাঘাত করেন। কিন্তু শ্যামা বলেন ‘তােমার কাছে দোষ করি নাই, দোষী আমি বিধাতার কাছে, তিনি করিবেন রােষ সহিব নীরবে’। কিন্তু প্রেমময় বিধাতা মুখ ফিরিয়ে রাখেন। যদিও বজ্রসেনের প্রাণ বারবার ব্যাকুল হয় এবং বলেন, “ক্ষমিতে পারিলাম না যে, ক্ষম হে মম দীনতা”।[৫]
এখানে উচ্চবিত্ত সমাজকে ভালােভাবে দেখা যায়। তাদের জীবন ও চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে প্রেমের লাঞ্ছনা কিন্তু একটু অন্যভাবে। এখানে ঈশ্বর অপরাধীকে শান্তি দেন কেননা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বৃহৎ স্বার্থে কখনােই জয় হয় না এবং ঈশ্বর তা সহ্য করেন না।
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা :
চণ্ডালিকা সামাজিক চিত্র চিত্রিত। এর ঘটনা নিম্নবিত্ত সমাজের। সমাজের নিম্নবিত্তদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী এর প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজের নিচু স্তরের মানুষ যাদের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণ উচ্চবিত্ত সমাজকে পতিত হতে হয় জীবনের সব আনন্দ, চাওয়া পাওয়া এই নিম্নবিত্ত সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। এই সমাজের মেয়ে চণ্ডালিকা।
সমস্ত প্রার্থীব বস্তু পাওয়ার বাধা তার মনকে ব্যাকুল করে। সে আনমনা হয়ে পড়ে। তার মা বারবার তাকে নিজের জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ও নিজের কাজে মন দিতে বলে। এমনই একটি দিনে গাভী শিশুকে স্নান করানাের সময় চণ্ডালিকার জীবনে আসেন দেব পুরুষ সন্ন্যাসী আনন্দ। চণ্ডালিকার জীবনে মহাপুরুষ আনন্দ, আনন্দ নিয়ে আসেন। তিনি চণ্ডালিকার কাছে তৃষ্ণার জল চান। কিন্তু চণ্ডালিকা শিহরিয়া উঠে বলে, আমি চণ্ডালের কন্যা, ”তােমারে দিব জল এ হেন পুণ্যের আমি নহি অধিকারিণী”। আনন্দ বলেন “যে মানব আমি, সেই মানব তুমি কন্যা, সেই বারি তীর্থ বারি”। এই উত্তর চণ্ডালিকার জীবনের মূল্যবােধকে এক নব চেতনা দান করে। সে তার মাকে বলে, ‘আমি চন্ডালি সে যে মিথ্যা ……..। রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য আমি সে দাসী নই। দ্বিজের বংশে চন্ডালি কত আছে, আমি নই চন্ডালী’। এ তো তার নবজন্ম। কিন্তু সেখানে সাধারণ মেয়ে চন্ডালী আনন্দকে সাধারণ প্রেমাস্পদ হিসাবে পেতে চায়। মাকে জাদু করে তাকে তার কাছে এনে দিতে বলে। অনেক কষ্টে মা নিজের জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে মহাপুরুষ আনন্দকে মন্ত্র সাধনার উচ্চমার্গ থেকে টেনে আনে। চণ্ডালিকার সাধারণ চাওয়া পাওয়ার আশা। তাতে এই মহান সাধকের লজ্জিত অবস্থা দেখে সত্যের আসল রূপ দেখে মনােবেদনায় আহত হয়। সে প্রকৃত জীবন দর্শন উপলব্ধি করে। এখানে দেহজ প্রেমের থেকে হৃদয় প্রেম বড় হয়ে ওঠে। নিজেকে জানার উপলব্ধি জাগে। আমি কারাের থেকে ছােট নই এই উপলব্ধি ঘঠে। অন্ত্যজ বলে নিজেকে আর ঘৃণা করতে শেখায় না। সে বলে ওঠে, “প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়, দিলে তার এত মূল্য, নিলে তার এত দুঃখ। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো– মাটিতে টেনেছি তোমারে, এনেছি নীচে, ধুলি হতে তুলি নাও আমায় তব পুণ্যলোকে। ক্ষমা করো। জয় হোক তোমার জয় হোক।” এখানেই চণ্ডলিকার মানসিক উত্তরণ কাহিনীর যবনিকা।
তিন কন্যার মূল কথা, ‘প্রেম’। কিন্তু দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে দেহজ নয়, দেহাতীত প্রেমে মানসিক চেতনার উত্তরণ ঘটিয়েছেন। চিত্রাঙ্গদা বলে, “যদি পার্শ্বে রাখাে মােরে সংকটের সম্পদে সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে….. আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দনী”। কিন্তু শ্যামা বলে, ‘তােমার কাছে দোষ করি নাই, দোষী আমি বিধাতার কাছে, তিনি করিবেন রােষ সহিব নীরবে, তুমি যদি না করাে দয়া সবে না’। এখানে শ্যামার দেহজ প্রেমের উত্তরণ ঘটেনি। তাই কবি তাকে ক্ষমা করতে পারেননি। লাঞ্ছিত প্রেম। সে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। পরিণতি ঘটেছে দুঃখের মধ্যে। কিন্তু মানুষের অধিকারে সচেতন হয়েছে চণ্ডালিনী, প্রকৃতি। তার প্রেম ভগবত প্রেমে লীন হয়েছে। সে বুঝেছে তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে তার প্রভুর আসন। জীবনের আদিমতার ধর্মকে ছাপিয়ে উঠলাে তার আত্মার শক্তি। চণ্ডালিকার ধারণা সার্থকতা লাভ করেছে মনস্তত্বের স্তরে স্তরে কাব্যসাহিত্যের ধ্যানের মধ্যে।
রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ভাবনায় নন্দনতত্ত্ব :
রবীন্দ্রনাথের নৃত্যভাবনা সম্পর্কে আলােচনার পূর্বে শিল্পকলায় তার নন্দনতন্ত্রের স্বরূপটি জানা প্রয়ােজন। নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টির মানসে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ-বর্জন, বিন্যাস, ঐক্য প্রভৃতির কথা বলেছেন। তার মতে মানুষ অন্ধভাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে না, তার সঙ্গে কল্পনার ছোয়া মিশিয়ে আপন মনের মাধুরী দিয়ে তাকে পরিবর্তিত করে নতুন রূপে প্রকাশ করে। প্রকৃতিতে যা দেখি তা প্রত্যক্ষ দেখি, কিছু শিল্পকর্মে দেখি সম্পূর্ণ নতুন চিত্র। মানুষের চেতনা প্রকৃতির বিচিত্র লীলার যে ইন্দ্রিয়দত্ত অনুভূতি পায় সেই অনুভূতিকে নিজস্ব একটা রূপ আরােপ কে নতুন ভাবে প্রকাশ করে। শিল্পীর মনে যা অপ্রত্যক্ষ ছিল তাই সেখানে প্রকাশ পায়। এখানে কাজ করে গ্রহণ বর্জন আত্মীকরণের নীতি। তাই তার ভাবনায়,
আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম “সুন্দর’,
সুন্দর হল সে।[৬]
তিনি বলেছেন যে, সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নয়। কেবল সাহিত্য কেন, কোন কলা বিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে প্রতীতি করা যায়, সাহিত্যে ও ললিতকলার ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষকে প্রভাতি করা যায়। সাহিত্যে ও ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ হয় প্রতীয়মান। কবির এই ভাবনা সকল শিল্পকার ক্ষেত্রেই প্রযােজ্য। যেমনটা আছে তেমনটাই ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য। গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়ে সেই তথ্য যখন কল্পনার রসে জারিত হয়ে স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে রূপাপ্তরিত হয় তখনই সেটা হয় বিন্যাস। আর গ্রহণ-বর্জন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটা সামগ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পকর্ম বা সুন্দর বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। রবীন্দ্রাথ এই সামগ্রিক ঐক্যকে বলেন সুমিতি। এই সুমিতিতে আর্টের সম্পূর্ণতা। শিল্পকলার মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ সুমিতি বিরাজ করে তাই আনন্দ দেয়। যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে।
নন্দনতত্ত্বের সাধারণ সূত্র ধরেই জীবনের উপকরণ গুলিকে সংযম সুসীমিত করে ঐক্যবদ্ধ করাও বিশেষ প্রয়ােজন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ধারার ভাবনার মূল লক্ষ্য ঐক্য। যদি কোনাে উপকরণ বড় হয়ে ওঠে ঐক্যকে বিনষ্ট করে তবে নান্দনিক আবেদন ব্যর্থ হয়। রসবাদের উপর দাড়িয়ে আছে নন্দন তত্ব। গ্রহণ বর্জন, বিন্যাস, ঐক্যের মাধ্যমে যে শিল্প সৃষ্টি হয় তাই নন্দনতত্বের মূল সুর। কাব্য, নাট্য, সংগীত (নৃত্য গীত বাদ্য), চিত্রকলায় সুসমন্বয়ে ঐক্য সৃষ্টি হল রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ভাবনা।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতার পর সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যুগে রামমােহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, প্রমুখ মনীষীদের দানে সামাজিক প্রগতি সূচিত হল। নাট্যশালা ও নাকটের পথ হল উক্ত। কিন্তু তখনও নৃত্যকলার পথ রুদ্ধ। কোনরকমে গ্রামবাংলায় লােকসংস্কৃতি টিকে রইল। শিক্ষিত সমাজের কাছে নৃত্য হল অবহেলিত। ফলে এর মান হল নিম্নগামী। শুধমাত্র রােজগারের আশায় মনােরঞ্জনের জন্য নিষিদ্ধ পল্লীতে এর ধারা হল সীমাবদ্ধ। শিক্ষিত সমাজের এই অবহেলাকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পথে গুরুতর ক্রটি বলেই গুরুদেব মনে করেছিলেন।
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা এই নৃত্যকলাকে শিক্ষার অন্যতম বাহন বলে স্বীকার করে নিয়ে শান্তিনিকেতনে একে মর্যাদার আসন দিলেন। নৃত্যগীতকে বুদ্ধি বৃত্তির সঙ্গে চিত্তবৃত্তির সংযােগ ঘটালেন। শুধুমাত্র নাচিয়ে তৈরি করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষা যেমন সমাজ জীবনকে উন্নত করে তােলে নৃত্যকলাও যেন তাই করে। তিনি তাকে দিয়েছিলেন মুক্তি, বৈয়াকরণিক এর বেড়াজাল থেকে। তার মতে গদ্য ভাষায় যেমন প্রচ্ছন্নভাবে ছন্দ থাকে, তেমনি মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য। নাচ শুধুমাত্র অভিব্যক্তি প্রকাশ নয় নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় জীবনের গভীর জীবন নৃত্যের একটি অখণ্ড ছন্দে ছন্দিত হয়ে এক সূত্রে বাঁধা পড়ে সৌন্দর্য বর্ধন করে। বিশ্বের মধ্যে যে ছন্দ আছে, গতি আছে, সেগুলিকে আশ্রয় করে স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করে তখনই সে এক নান্দনিক সৌন্দর্য বর্ধন করে। মানুষ যুক্ত হয় বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে। সেই যােগই নান্দনিক তত্বের বড় বিশেষত্ব। জীবনের এই ছন্দ বােধই কবিকে চালিত করেছে, গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত এক অবিচ্ছেদ্য বিবর্তনের পথে। সােনার তরী, বসুন্ধরা’, চিত্রা’, পুরবী, “মহয়া প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তার নৃত্য ভাবনার চিত্র ফুটে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে রাবীন্দ্রিক নন্দনতক্রের আভাস পাওয়া যায়। নন্দন তত্ব সম্পর্কে তার ধারণা, বিজ্ঞান জগতের বিচারের মত করে সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। সৌন্দর্য জিনিসটা অনুভূতির ব্যাপার। একজনের যে জিনিসটা ভাল লাগে অন্যজনের সেটা ভালাে নাও লাগতে পারে। রুচি ভেদে ভালাে লাগা আর ভালাে না লাগার পার্থকা থাকতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে গাছপালা, ফুল ফল, পাহাড়, নী আছে। কারাো পাহাড় ভালােলাগে, কারুর ভালাে লাগে সমুদ্র। তবে মতভেদ থাকলেও মতবিরােধ নেই। বিরােধ কেবল মানুষের সৃষ্টিতে, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও নৃত্য ধারায়। তবে কাব্যে সাহিত্যে যাকে সুন্দর বলা হয়, জীবনের ক্ষেত্রে তাকে সবসময় সুন্দর নাও বলা যেতে পারে। বাস্তব জীবনে মৃত্যু বিচ্ছেদ কাম্য নয়, কিন্তু কাব্যে, সাহিত্যে নৃত্যগীতে, বিয়োগান্ত বিষয়বস্তু বেশি আকর্ষণ করে। তাই সর্বকালের সর্বদেশের সেরা সৃষ্টি বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়ে। রবীন্দ্র নন্দনতত্বের মধ্যে যে মূল ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তা হল নিজেকে প্রকাশ করা। মানুষের মনের রাজ্যে প্রতিনিয়ত নানাভাবের নানা অনুভূতির জন্ম হচ্ছে। তাই গুরুদেবের ভাষায়, “আপনাকে সে জানা আমার ফুরাবে না”। এই জানাটাই মানুষ প্রকাশ করতে চায়। রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। এই প্রকাশের তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নৃত্যাধারা।
নৃত্য সম্পর্কে কবির ধারণা, যখন আদি দেবের আহ্বানে সৃষ্টি উৎসব জাগল, তখন তা প্রথম আরম্ভ হলাে আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্য। সূর্য চন্দ্র আজ বিরাম পেল না। ষড়ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলােকে আলােকে অন্ধকারে যুগল নৃত্য, নরলােকে অশান্ত জন্ম-মৃত্যুর নৃত্য। সৃষ্টির আদিম ভাষাই নৃত্য। মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে, কেননা তার দেহ ছন্দ রচনার উপযোগী। আবার নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহ সঞ্চালনের অর্থহীন সুষমায়, তাতে কেবল ছন্দের আনন্দ। তাই তিনি বলেছেন যে, দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে, দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে জীবনের প্রয়ােজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে নৃত্য বলে আখ্যায়িত করা হয়। নৃত্যে ছন্দের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুদেবের ভাবনা, রূপ সৃষ্টির প্রবাহই তাে বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণু তত্ত্বে সেকথা সুম্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহ আলাে দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা যায় না। কিন্তু বিদ্যুৎ কণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে চৈতন্যের দ্বারে আঘাত করে, তখনই প্রকাশ পায় রূপ, কোনােটা দেখা যায় ঘােলা হয়ে, কোনটা সীসে। বিশেষ সংখ্যক মাত্রা ও বিশেষ বেগের গতি এই দুই নিয়ে ছন্দ, সেই ছন্দের মায়া মন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত। বিশ্ব সৃষ্টির এই ছন্দ রহস্য মানুষের শিল্প সৃষ্টিতে। সংযত ঘন আবেগের প্রকাশ দ্বারা রূপ সৃষ্টি করাই শিল্পকলার আদর্শ। গীত সহযােগে দেহভঙ্গির মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য সু-সামঞ্জস্য সহকারে মনের সংযত আবেগের বাহ্য অভিব্যক্তি এবং তার দ্বারা অনির্বচনীয় রূপ সৃষ্টিতে ভারতীয় নৃত্যের পরিপূর্ণতা। ভারতীয় নৃত্যে সংগীত এক অপরিহার্য অঙ্গ, সেই সংগীতের ধারায় অবগাহন করে অনির্বচনীয় আনন্দে পুলিকত হয় চিত্র।
নৃত্য সেই আনন্দ-বেদনাকে দেহভঙ্গির সঙ্গীতে ছন্দের মধ্য দিয়ে অপরূপ রস রূপে সংবেদনশীল রসিক চিত্তে সংক্রমিত করে। এইখানে ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক ভাবাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্র দর্শনের মিল দেখা যায়। যুগের নাট্যশাস্ত্রকারগণ অভিনয় দর্পনে কল্পনায় যে নটরাজের ছবি এঁকেছেন, তা হল, অঙ্গিকং ভূবন যস্য, বাচিকং সর্ববাত্ময়ম, আহার্যং চন্দ্রতারাদি, তং নুম সাত্ত্বিকং শিবম। তার সঙ্গে কবি কল্পনা একাত্মা হয়েগেছে। কবি বলেন,
‘নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।
তৰ নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে-দুখে হয় তরঙ্গময় তােমার পরমানন্দ হে’।[৭]
যদিও রবীন্দ্র নৃত্য ধারা ভারতীয় নৃত্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, তবুও কোনও ক্ষেত্রেই তিনি শান্ত্রের অন্ধ গোঁড়ামিকে মেনে নেন নি। বৈয়াকরণিক রীতি নিয়মের শৃংখলে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যকে তিনি ব্যাকরণ শৃংখল মুক্ত করতে চেয়েছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি রাগরাগিণীর গোঁড়ামি থেকে মুক্তি দিয়েছেন তার রচিত সংগীতকে। নৃত্যের ক্ষেত্রেও তিনি তাই করেছেন।
তথ্যসূত্র
১। অমিতা সেন-শান্তিনিকেেতনে আশ্রম কন্যা
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ক্ষণিকা
৩। শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী-স্মৃতি কথা
৪। প্রতিমা দেবী – নির্বাণ
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- শ্যামা
৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- শ্যামলী
৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী (অষ্টাদশ খণ্ড)

