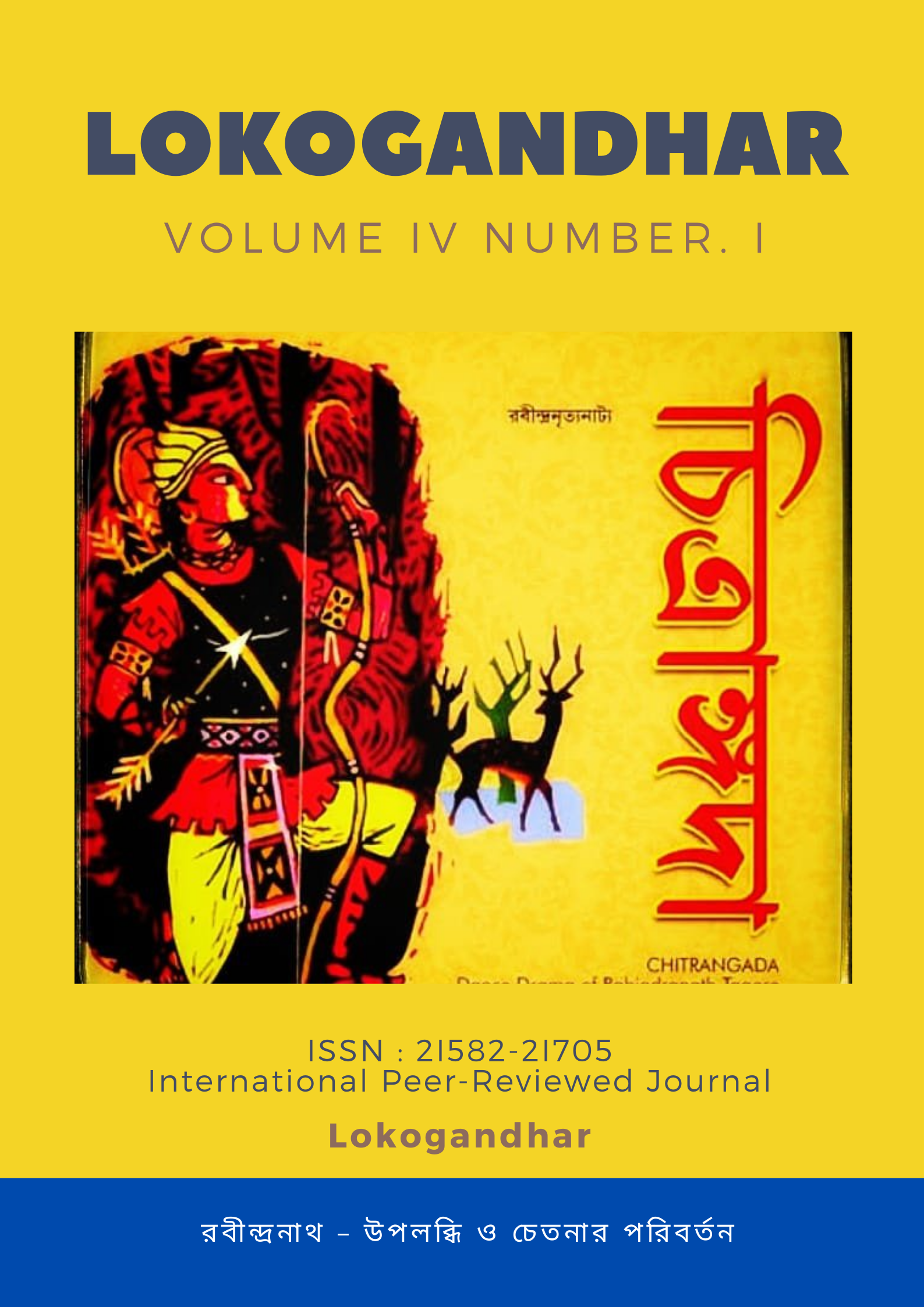Rabindranath – Changes in Perception and Consciousness
Dr. Pratiti Pramanik De
Abstract
In art creation, be it literature or music, its main form is aesthetics. The important aspect of this aesthetics is expression. The expressed form is not always acceptable to the viewer or listener in exactly the same perception with which the artist has created his art. The viewer also adds some of his own perception. Film is essentially a visual art. Until the 1920s, silent films were only visual art. Then he spoke to him. As a result, audibility has been combined with visibility. Films have become an almost universal art form with the arrangement of the audio of the words and the atmosphere of the music to be painted on celluloid. The name Rabindranath flows in every drop of blood in the veins of Indians especially Bengalis at every moment. When the Rabindrasangeets were performed before the copyright lapsed, they were performed according to the notational instructions and with the correct intonation. In that case the songs had to be practiced properly. But to the present generation, Rabindra Sangeet is gradually becoming comprehensible. One of the main reasons for this is lack of copyright. As a result, there is a growing tendency to perform songs arbitrarily without following any rules.
Key notes : Art, Aesthetic, perception, Rabindrasangeet, Copyright.
১
রবীন্দ্রনাথ – উপলব্ধি ও চেতনার পরিবর্তন
ড. প্রতীতি প্রামাণিক দে
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ ,সংগীত বিভাগ
শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তা সাহিত্য বা সঙ্গীত যাই হোক না কেন তার প্রধান স্বরূপটি হল নন্দনতত্ত্ব।এই নন্দনতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল প্রকাশ। শিল্পী যে উপলব্ধি নিয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টি করেছেন, সেই প্রকাশিত রূপ হুবহু একই উপলব্ধিতে দর্শক বা শ্রোতার কাছে সবসময় গ্রহণীয় হয় না। দর্শক তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিরও কিছুটা মিশ্ৰণ ঘটান ।
সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নাটক ইত্যাদি শিল্পমাধ্যমগুলির তুলনায় চলচ্চিত্র প্রাচীন নয়, বরং এতটাই নবীন যে এর জন্মলগ্নও আমরা চিহ্নিত করতে পারি, কিন্তু জনমানসে এর ব্যাপক অভিঘাত, প্রভাব ও স্বীকৃত আমাদের আশ্চর্য করে। একশো বছর আগে বিজ্ঞানীর যন্ত্র আর সাধারণের খেলনা হিসাবে যখন এর জন্ম হয় তখন কেউই ভাবতে পারেননি যে ওই সামান্য সূচনাই অদূর ভবিষ্যতে ক্রমশ ব্যপ্ত হবে অপরিমেয় বিশালতায় উচ্চমানের শিল্পে। চলচ্চিত্র হল সবচেয়ে বাস্তবমুখী শিল্প, সবচেয়ে শক্তিশালী বাস্তবতার মাধ্যম। এই চলচ্চিত্রে বিভিন্ন শিল্পকলা জড়িত। যেমন সাহিত্য, নাটক, অভিনয়, সঙ্গীত ইত্যাদি। এই সমস্ত একসাথে মিলিত হয়ে একটি নতুন শিল্পকলার রূপান্তর হয়। চলচ্চিত্র হল একবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পমাধ্যম। এটি আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে আধুনিক, কনিষ্ঠতম মাধ্যম। বর্তমানে সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ। সভ্যতার পথপরিক্রমায় শিল্প একমাত্র না হলেও এক বড় নির্ভর পর্ব। পর্ব থেকে পর্বান্তরে শিল্পের কত না রূপ। কতই না তার রূপান্তর। চলচ্চিত্র শিল্পের বয়স যদিও একশো বছর অতিক্রান্ত কিন্তু এরই মধ্যে সে শ্রেষ্ঠতর শিরোপাটি আপন অধিকারে নিয়ে আসতে পেরেছে।
চলচ্চিত্র মূলতঃ ভিস্যুয়াল শিল্প। ১৯২০-র বছরগুলি পর্যন্ত নির্বাক চলচ্চিত্র ছিল শুধুই দৃশ্যশিল্প। তারপর তার সাথে কথা যুক্ত হয়েছে। তার ফলে দৃশ্যতার সঙ্গে শ্রাব্যতাও যুক্ত হয়েছে। কথার শ্রাব্যতার সঙ্গে সঙ্গীতের আবহ সেলুলয়েডে এঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় চলচ্চিত্র প্রায় একটি সর্বাঙ্গীন শিল্প হয়ে উঠেছে। সব শিল্পেরই দুটো দিক থাকে, তার রূপ বা ফর্ম আর তার বস্তু কনটেস্ট। বস্তুর দিক থেকে প্রায় সব শিল্পেরই একটা মিলের জায়গা থাকে। চলচ্চিত্র যেমন গল্প বলে সাহিত্যের কোন কোন সংরূপও
২
তেমনই গল্প বলে। মৌলিক মাধ্যম নয় বলে অন্য সমস্ত মাধ্যম থেকে অকৃপণভাবে নিয়ে আত্মসাৎ করে চলচ্চিত্র আগ্রস্থ হয়েছে।
যতদিন সিনেমা ছিল নিছক দৃষ্টিসুখের উপকরণ, ততদিন জনসাধারণের সঙ্গে তার মানসিক সংযোগ সিনেমা যতই নাটক ও সাহিত্যের কাছাকাছি চলে গেল ততই সেটি বেশি করে উচ্চমার্গের দর্শকের সঙ্গে মস্তিষ্কজাত সংযোগ গড়ে তুলল। সেই ক্ষেত্রে সাধারণ দর্শকের মনসংযোগ আকর্ষণ করার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা একটু কঠিন হয়ে পড়ল। তা সত্ত্বেও পরিচালকদের বিশেষ কৃতিত্বের ফলে সেইসব সাহিত্যধর্মী চলচ্চিত্রও কিছু সময় সঙ্গীতের প্রযোগে বা দৃশ্যের বুননে জনসাধারণের সঙ্গে মানসিক সংযোগ গড়ে তুলল। সিনেমা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এত বেশী গল্প বলতে শিখল যে সেখানে ছবি তার নিজস্বতায় দুর করার জোর অনেকটা হারিয়ে ফেলল। দর্শকরা ধরে নিলেন, গল্প উপন্যাস পড়বার বদলে সেই গল্প-উপন্যাসকে তিনি এখন দেখছেন, তাঁদের পড়া গল্পে আর চলচ্চিত্রে। এইটুকুই যা প্রভেদ। কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলোকে এখন আর ভাবতে হচ্ছে না। তাঁদের সজীব পরিক্রমার মাধ্যমে যেসব চরিত্র এখন তারা গল্পের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সেই ঘটনা, এ দুটিকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারাই যেন ফিল্মের একমাত্র মহিমা হয়ে দাঁড়াল অনেকের কাছে।
রবীন্দ্রনাথ নামটি ভারতীয়দের বিশেষভাবে বাঙালির মনেপ্রাণে প্রতিটি রক্তবিন্দুতে শিরায় উপশিরায় প্রবহমান প্রতিটিক্ষণে। নামটির সাথেই কোথাও গভীর উপলব্ধি জড়িয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে এই একবিংশ শতাব্দীতেও তিনি সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন বর্তমান প্রজন্মের মধ্যেও। বাঙালির আধুনিক রুচি ও মানস গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টা। সৃজনশীলতাতেই তার আসল পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে বলেছেন –
একটা দিক হচ্ছে তথ্য আর একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে তাকে সেই হচ্ছে সত্য। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।[১]
রবীন্দ্রনাথ একসময় বাংলার সংস্কৃতির উপর বিদেশি প্রভাব সম্পর্কে খুব ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হত বিদেশি প্রভাবের ফলে
৩
বাংলা তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলবে। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিতে যে সৌন্দর্য যে মাধুর্য আছে তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করলে দর্শক বা পাঠক বা শ্রোতা তার সাথে নিজের উপলব্ধির মিশ্রণ ঘটিয়ে তার স্বাদ নিতে চেষ্টা করেন এবং সেখানেই সৃষ্টিকর্তার আত্মোপলব্ধি পরিতৃপ্তি লাভ করে। তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী, চেতনা ও উপলব্ধির বিশেষ কিছু পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। এর একটি বিশেষ কারণও আছে- সেটি হল ২০০১ সালে কপিরাইট উঠে যাওয়া। বিংশ শতকে চলচ্চিত্র বা সংস্কৃতি জগতে রবীন্দ্রসৃষ্টিকে যখন বিশুদ্ধভাবে ব্যবহার করা হত সেখানে কিছুটা রবীন্দ্রভাবনার সরাসরি প্রভাব পড়ত। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্বরলিপিকে নির্দেশ অনুযায়ী পালন করেই সঙ্গীতগুলি পরিবেশিত হত, তার ফলে গায়নশৈলী, বাচনভঙ্গী এমনকি সর্বাঙ্গীনভাবে গানটির ভাবও সুন্দরভাবে ফুটে উঠত সহজেই। একইসঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গের প্রয়োগও হত খুব পরিমার্জিতভাবে। অপরদিকে রবীন্দ্রসাহিত্য অবলম্বনে যে চলচ্চিত্রগুলি নির্মিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে সেই চলচ্চিত্রগুলি দর্শনের মাধ্যমেই দর্শকের পড়া হয়ে যেত। অর্থাৎ রবীন্দ্রভাবনা অনুযায়ী চলচ্চিত্রগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নির্মিত হত, খুব প্রয়োজন ছাড়া মূল গল্পের খুব বেশি পরিবর্তন করা হত না। তবে একথাও ঠিক সাহিত্যের ভাষা আর চলচ্চিত্রের ভাষা এক নয়। যখনই কোন সাহিত্যকে চলচ্চিত্রের জন্য সংলাপে পরিবর্তিত করতে হয় সেক্ষেত্রে মূল গল্পটির পটভূমির পরিবর্তন না হলেও দৃশ্যমানতার অনেক পরিবর্তন করতে হয় চিত্রকারকে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য। যেমন- সিনেমার লোকেজন বাছা, কিছু অতিরিক্ত সংলাপ সংযোজন, এমনকি গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তের প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তন। উদাহরণ স্বরূপ – সত্যজিৎ রায়ের “তিনকন্যা” ছবির ‘পোষ্টমাষ্টার’-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখকের মূল কাহিনীর কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন পরিচালক। এই ছবিতে ঘটনার খুব একটা প্রাচুর্য দেখাননি বটে, কিন্তু অনেকগুলি চরিত্র পর্দায় এনেছেন। ফলে রতন ও পোস্টমাস্টারের পরস্পরের প্রতি যে সংবেদনশীল অনুভূতি গল্পে বজায় ছিল, সিনেমায় সেটি শেষ দৃশ্যের আগে পর্যন্ত অনুপস্থিত। শেষ দৃশ্যে রতনের কান্না ও বখশিস ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় অনুভূতিটি ফুটে উঠেছে। এই বদল করার সপক্ষে পরিচালক যে যুক্তি দিয়েছিলেন –
‘‘রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্পে আছে যা অনুভূতির ক্ষেত্রে একেবারেই ভিক্টোরীয় যুগের। ধরুন ‘পোস্টমাস্টার গল্পটির কথাই। এর সমাপ্তিটা আমার কাছে বড্ড আবেগপ্রবণ মনে হয়েছে। সেটা আমার কাছে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব, কেননা আমি তো বিংশ শতাব্দীর মানুষ, বিশেষ একটা পরিবেশে মানুষ হয়েছি, বিশেষ ধরণের কিছু প্রভাব আমার ওপর পড়েছে। কাজেই গল্পের
৪
পরিসমাপ্তিটা আমি ঘটালাম খানিকটা বিরসতা সৃষ্টি করে, তবে পরিণামটাকে নিজের পথেই আমি চলতে দিয়েছি। ছবিতে মেয়েটি তার বেদনাকে প্রকাশ করার বদলে বরং গোপনই করেছে। শুধু কুয়ো থেকে জল তোলবার সময় তাকে আপনারা কাঁদতে দেখেছেন। কিন্তু সেই তার ডাক পড়েছে অমনি সে চোখের জল মুছে ফেলেছে। ১৯৬০ সালে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন এমন একজন বিংশ শতকীয় শিল্পীর – আমার এইটাই হল ব্যাখ্যা। গোঁড়ারা এসবে আপত্তি করবেন জানি, কিন্তু আমি এটা করেছি শিল্পী হিসাবে নিজের অনুভবকে ব্যস্ত করে জন্যই রবীন্দ্রনাথের গল্প আমি নিয়েছি সেটার প্রকাশমাধ্যম রূপেই ব্যাখ্যা আমার নিজস্ব।”[২]
অর্থাৎ এর থেকে আমরা বুঝতে পারি কোথাও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উপলব্ধি ও সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটের উপলব্ধি কিছুটা আলাদা। চিত্রকার দর্শকের কাছে কোনটি বেশী গ্রহণযোগ্য হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁর উপলব্ধিটি তুলে ধরার চেষ্টা করেন তাঁর চিত্রনাট্যে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর এক বিশেষ হাওয়াবদল হয় সাহিত্যভাবনা, চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। যেহেতু আজকের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ, সেহেতু তাঁর নির্মাণ নিয়েই প্রধান আলোচনা। অনেক ছবির মধ্যে কেবল দুটি ছবিকে বেছে নিয়েছি আলোচনার জন্য, শুধু আলোচনা নয়। এক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা বলাই শ্রেয়। দুটি চলচ্চিত্র হল-
(১) সত্যজিৎ রায় নির্মিত চারুলতা (১৯৬৪) ও অগ্নিদেব চ্যাটার্জি নির্মিত চারুলতা ২০১১ (২০১২)
২) সৌরেন সেন নির্মিত চিত্রঙ্গদা (১৯৫৫) ও ঋতুপর্ণ ঘোষ নির্মিত চিত্রাঙ্গদা (২০১২)।
রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা চলচ্চিত্রটি তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি রচনা করেন ১৯০১ সালে, সত্যজিৎ ১৯৬৪ সালে গল্পটির চিত্ররূপ দেন। ‘নষ্টনীড়’ ও ‘চারুলতা’ দুই ক্ষেত্রেই মূল চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ, চারু, ভূপতি, অমল, মন্দা ও উমাপদ। সত্যজিৎ এই চলচ্চিত্রের তৈরির ক্ষেত্রে ‘ক্লাসিক্যাল ষ্টাইল’ এর কথাই ভেবেছেন। মূল কাহিনীতে যে ত্রিকৌণিক জটিল রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন, সত্যজিৎ তাকেই রূপান্তরিত করেছেন প্রধান পরিকাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেই। অমলের চরিত্রের গভীরতা তিনি কমিয়েছেন, কিন্তু চারুর নৈসঙ্গের যন্ত্রণাটুকু যেভাবে সত্যজিৎ হাইলাইট করেছেন তাতে তার সুগভীর অন্তদ্বন্দ্বটা অনেক বেশি দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মূল কাহিনীতে বর্ণিত অনেক ঘটনা আবার সিনেমায়
৫
বাদ পড়েছে। যেমন ক্রুদ্ধ ভূপতির আকস্মিকভাবে নিজের লেখার খাতাগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া, প্রি-পেড টেলিগ্রামের জবাব হাতে পেয়ে চারু অমলের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভূপতির অবগত হওয়া, সাহিত্যিক মাধ্যমে এগুলি অত্যন্ত সহজভাবে প্রকাশ করা গেলেও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এগুলি হয়ত অতিনাটকীয়তা হিসাবেই প্রকাশ পেত। লেখকের ভাবনার সেই মৃদু অথচ গভীর আবেদন সিনেমার মূল উপজীব্যের মধ্যেও যথাযথ বজায় রয়েছে। সত্যজিৎ তা বজায় রেখেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পাঠবৃত্তকে নিটোল রাখার প্রয়োজনেই। আবার অগ্নিদেব চ্যাটার্জি নির্মিত চারুলতা ২০১১ চলচ্চিত্রে পরিচালক দেখিয়েছেন বর্তমানেও চারুর মতো কোন একটি একাকী নারীর কাহিনী। যা রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ গল্পের চারুলতার অনুপ্রেরণায় নির্মিত।
১৯৫৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘চিত্রাঙ্গদা’ কিন্তু ঠিক নৃত্যনাট্য নয়। বরং বলা যেতে পারে সৌরেন সেন ও হেমচন্দ্র চন্দ্র এই পরিচালকদ্বয় “চিত্রাঙ্গদা’ অবলম্বনে এক চলচ্চিত্রই করতে চেয়েছিলেন, যার ভিত শুধু চিত্রাঙ্গদা আর অর্জুনের প্রেম নয়, বরং রবীন্দ্ররচনা ‘চিত্রাঙ্গদা’-র অন্তঃস্রোতে যে নারীবাদ আছে সেটার ওপরেই প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁরা। যুগ যুগ ধরে চিত্রাঙ্গদা আছেন মহাভারতে মাত্র দু-তিনটি শ্লোকের মাধ্যমে, তাকে পাশে রেখে রবীন্দ্রনাথ তার নিজের ভাবনায় রচনা করলেন নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা”। আর সেই নৃত্যনাটাকেই পাথেয় করে ঋতুপর্ণ বানিয়েছিলেন একটা ইচ্ছের ছবি চিত্রাঙ্গদা : দ্য ক্রাউনিং উইশ। এই ছবিকে বাংলা বা ভারতীয় সিনেমা বললে একটু কমই বলা হবে। বিশেষতঃ গোটা বিশ্বে সমকামী আন্দোলন যেভাবে জোরদার সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এই চলচ্চিত্রটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের ছবি বলা যেতেই পারে। আদতে এটি একটি সম্পর্কের ছবি, ইচ্ছেপূরণের গল্প। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাটোর শেষটা আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত এক নারী ‘পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সে-ও আমি নই। ঋতুপর্ণর চিত্রাঙ্গদায় এই প্রত্যাখ্যান আসে অনেক পরে।
কাহিনী অনুযায়ী মণিপুর রাজার কন্যা জন্মাল, কিন্তু তাকে ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ও রাজবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হল। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা তার বাবার ইচ্ছায় নারীদেহে পুরুষালী কর্মকৌশল রপ্ত করেছিলেন। তারপর চিত্রাঙ্গদা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে প্রেমে পড়ল বীর অর্জুনের। পুরুষের বেশে থাকা নারী প্রেমে পড়ল পুরুষের। এরপর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের মাধ্যমে নারীময়ী চিত্রাঙ্গদার সাথে মিলন হয় অর্জুনের। অর্থাৎ তার নারীসুলভ হয়ে ওঠার ইচ্ছাপ্রকাশ পায়, সেও এক ইচ্ছপূরণ।
৬
ঋতুপর্ণর চিত্রাঙ্গদায় নৃত্যপরিচালক রুদ্র (ঋতুপর্ণ ঘোষ) যেন সেই চিত্রাঙ্গদা। পুরুষ শরীরে জন্মানো বাবা মায়ের ইচ্ছের এক প্রযুক্তিবিদ কিন্তু মানসিকভাবে এক নারী যার ধ্যান জ্ঞান তার নাচ । বিশ্বকবির জন্মসার্ধশতবর্ষে তার দলে ‘চিত্রাঙ্গদা’-র মহড়া দিচ্ছেন মঞ্চস্থ হবে বলে। এমন সময়েই তার দলে অর্জুনের মতো প্রবেশ ঘটে মাদকাশক্ত, জোচ্চোর, প্রতিভাবান পারকাশনিষ্ট পার্থর (যীশু সেনগুপ্ত)। রুদ্র যেমন এই নৃত্যনাট্যের পরিচালক তেমনই প্রেমের দেবতা মদনের চরিত্রাভিনেতা। আর প্রেমের দেবতা মদনও এখানে নারীবেশী। যেন ইচ্ছের মাধুরী। ধীরে ধীরে রুদ্র আর পার্থ ঘনিষ্ঠ হয়, কিন্তু রুদ্র যে পুরুষ দেহে আবৃত মনে প্রাণে এক নারী ! রুদ্র পার্থর প্রেমে পড়ে, সংসার পাতার স্বপ্ন দেখে। রুদ্র পৌঁছে যায় অপারেশন টেবিলে। কিন্তু যে রুদ্রর সাথে প্রেম করল পার্থ, সে বিয়ে করল নাট্যগোষ্ঠীর কম্ভুবীকে (রাইমা সেন)। মহাভারতে ঠিক যেমন অর্জুনকে পেতে চিত্রাঙ্গদার রূপান্তর চাইতে হচ্ছে মদন দেব-এর কাছে আর মদন দেব সেই প্রার্থনা পূর্ণ করছেন। তাকে পরিণত করেছেন নারীতে, কুরূপা থেকে সুরূপাতে। স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাটাখানি উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে একটি ভূমিকায় জানাচ্ছেন কবিগুরু-
“অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধহয় চৈত্রমাস হবে। রেললাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগুনী সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা মনে এল যে, আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলো তার রক্তের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরু প্রকৃতি তার অন্তরের নিগুঢ় রসসঞ্জয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অগ্রগলভ ফলসন্তারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসানোর অভিযোগে সতীন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্যসিদ্ধ করার জন্য যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। এই দানেই আদার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতায় মালিন্য নেই, এই চারিত্রশক্তি জীবনের খুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়, অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক। এই ভাবনাটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ ইচ্ছা তখনই মনে এলো। সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনী
৭
কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার সমতুল মুহূর্ত যদি সনাক্ত করতে হয় তো উদ্ধৃত করতে হবে সেই যেখানে অর্জুন বলছে, কুরূপা চিত্রাঙ্গনাকে-
ক্ষমা করো আমায়
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে,
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী।
যে প্রত্যাখ্যানে চিত্রাঙ্গদা কান্নায় গেয়ে উঠেছে ‘রোদন ভরা এ বসন্ত, সখী, কখনো আসেনি বুঝি আগে।
রুদ্র-পার্থর বিচ্ছেদ রবিঠাকুরের স্ক্রিপ্ট মেনে নেয় জীবনের স্বভাব ও নিয়মে। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার মতো রুদ্র-পার্থর মিলন হয় না। রুদ্র ফিরে আসে বাবা মায়ের সংসারে, যেখানে একদিন বজ্রপাত ঘটিয়ে সে ঘোষণা করেছিল মেয়েতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। প্রেমিক প্রত্যাখ্যানের থেকে এও কিন্তু কম ট্রাজিক মুহুর্ত নয়।
মহাকাব্যিক প্রেমের রাবীন্দ্রিক নৃত্যনাট্যে এভাবেই অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছেন ঋতুপর্ণ। অন্তর্ঘাত কোথায় নেই? গানের কথাগুলিই ধরা যাক। ছেলে থেকে মেয়ে হওয়ার জন্য অপারেশন টেবিলে রুদ্র। সামনে সবুজ মাস্ক পরা ডাক্তার, ওপরে উজ্জ্বল আলো, ব্যাকগ্রাউন্ডে গান ‘বঁধু, কোন আলো লাগল চোখো। আর এই অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবমাননা নয়, বরং সেগুলির অমিত শক্তির দিকেই যেন নির্দেশ করেন পরিচালক।
‘চিত্রাঙ্গদা’ ছবিতে রুদ্র আর পারকশনিষ্ট পার্থর সম্পর্ক থেকে এক মানবী গহন ইচ্ছের গল্পর বলা শুরু। সে গল্প, ছবি জুড়ে রুদ্রর নিজের সঙ্গে নিজের কথাচারিতায় কোলাজে এও মনে হয়, এক আমির সাথে অন্য আমির কথা ও উপকথনে নারীর বহু জন্মান্তরের গল্প বলেছেন ঋতুপর্ণ। ক্যামেরার সামনে কদ্রর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, ক্যামেরার পিছনে নির্মাতা নিজেই। নিরাময় কেন্দ্রে যার নাম করতে গিয়ে বলা হয় বা নার্সকে রুদ্র তার নিজের দেওয়া নাম বলে, কিন্তু নার্স জানিয়ে দেয় ওই নামে কেউ নেই, ছিল না কোনোদিন, ওটা রুদ্রর হ্যালুসিনেশন, ইচ্ছেবদলের পালে লাগে হাওয়া প্রেমিক পার্থর জন্য শরীর কাটাছেঁড়ার পর প্রত্যাখ্যাত হয়ে রুদ্রর মনে পড়ে আরও একবার চিত্রাঙ্গদার পরিণতির কথা। ছবির শেষে, সমুদ্রতীরের ভোরের আলোয় একটি সংলাপ ‘কোন রূপান্তরই সম্পূর্ণ নয়, পদ্ধতিটা চলতেই থাকে। ঋতুপর্ণ উড়ান দেন মহাকাব্যের ডানায়। যখন শারীরিকভাবে রুদ্রর
৮
নারী হয়ে ওঠার উদ্যোগ অস্ত্রোপচারকে মেনে নিতে পারে না পার্থ। কারুর শরীরে সার্জারীতে ওর গোড়া থেকেই আপত্তি ছিল, ও লিঙ্গান্তরিত হতে সেই বিতৃষ্ণা চরমে পৌঁছল।
রুদ্রকে দেখতে হাসপাতালে গেল যখন ও, ততদিনে নাট্যদলের সুন্দরী নায়িকা কস্তুরীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। “চিত্রাঙ্গদা: দ্য ক্রাউনিং উইশ’ খুবই নতুন ধরণের সাহসী কাজ। লিঙ্গ সমস্যা নিয়ে কাজ বলেই হয়ত ছবির সংলাপের এক তৃতীয়াংশ ইংরাজীতে। বিখ্যাত নৃত্যনাট্যের লিঙ্গ রূপান্তরের সঙ্গে এই সময়ের পরিস্থিতিকে বাঁধতে একটা কার্যকর কাহিনীও উদ্ভাবন করেছেন ঋতুপর্ণ। সবচেয়ে করুণ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় রুদ্রর নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক। যেটা মনোবিদের সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনে প্রতিষ্ঠা করা গেছে। বিশেষ করে পার্থর প্রত্যাখ্যানের পর সে সরল যুক্তি দিয়ে (“ও তো বারণই করেছিল”) পরিস্থিতির সামাল দেয়। রুদ্র। চিত্রাঙ্গদা দেখে কেন জানিনা মনে হয় সংবেদী সংলাপ ও কল্পনার প্রয়োগ এবং ব্যবহারে ঋতুপর্ণ অনেক বেশী দক্ষ সৃষ্টিশীল কাহিনী সংগঠনের চেয়ে। চিত্রাঙ্গদা আচ্ছন্ন হয়ে আছেন অসাধারণ সব অভিনয়ে। সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে অঞ্জন দত্তের (মনোবিদ) সম্ভবতঃ অদ্যাবধি তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয়। প্রথমতঃ ওঁর মেক আপটাই অসাধারণ, অঞ্জনের পূর্ণ রূপান্তর। সঙ্গে হাসি মাখানো নম্র স্বরক্ষেপ, ব্যঞ্জনাময় চাহনি বাবার ভূমিকায় দীপঙ্কর দে ও মায়ের ভূমিকায় অনসূয়া মজুমদারের অভিনয়ও অসাধারণ। .
এই ছবির অন্যতম উপাদান ছবির সিনেম্যাটোগ্রাফি, যার নেপথ্যে আছেন অভীক মুখোপাধ্যায়। হাসপাতালের জানালা দিয়ে শহরের নৈশচিত্র, চিত্রাঙ্গদার মঞে মায়াময় আলোর বিম নেম আসা ইত্যাদি এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছে ছবিকে। যোগ্য সঙ্গত দিয়েছে। অর্থ্যাকমল মিত্রের সম্পাদনা, দেবজ্যোতি মিশ্রের সুরারোপ। তাঁর সুরারোপে চমৎকার ঝাঁঝ, প্যাশন ও বর্ণময়তা। চিত্রাঙ্গদার মধ্যে যে সুররিয়েল আবহ ছিল সেটার জন্য সঙ্গীত পরিচালক ব্যবহার করেছেন আর্মেনিয়াম উড়ুইক ডুডুক। মহাভারত আর পোষ্টমর্ডাণ চিত্রাঙ্গনার মাঝে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সবকিছুর মধ্যে থেকে একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছেন পরিচালক। শুধুমাত্র যে চিত্রনাট্য নির্মাণ, পরিবেশনের পরিবর্তন নয়, বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এমনকি পোশাক-আশাকের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। এর সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয় উপলব্ধি বা চেতনা। এই উপলব্ধিও পারিপার্শ্বিক সমাজের বা পরিবেশের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সমাজের উপযোগী করেই চিত্রকাররা চিত্রনির্মাণ করেন যাতে দর্শক প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে ওই সময়টুকু সম্পূর্ণভাবে ছবির কাহিনীর সাথে সমসাময়িক পটভূমি বা নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন
৯
করতে পারেন।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সমপরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কপিরাইট উঠে যাওয়ার পূর্বে গানগুলি যখন পরিবেশিত হত তখন স্বরলিপির নির্দেশনানুযায়ী ও গায়নভঙ্গী সঠিকভাবে বজায় রেখে পরিবেশন করা হত। সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে গানগুলিকে অনুশীলন করতেও হত। কিন্তু বর্তমান প্রজনোর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত দুর্বোধ্য থেকে ক্রমশঃ সহজবোধ্য হয়ে উঠছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ কপিরাইট না থাকা। যার ফলে কোনরকম নিয়ম না মেনেই যথেচ্ছভাবে গানগুলি পরিবেশন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষা না নিয়েই কেবলমাত্র প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে ও বিভিন্ন ট্র্যাক ব্যবহার করে গানগুলি প্রয়োজনের অতিরিক্ত যন্ত্রানুষঙ্গের সাথে পরিবেশন করা হচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টিকর্তার যে উপলব্ধি তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়। যে উপলব্ধি বা ভাবনা নিয়ে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত তৈরি হয়েছিল তার কথা ও সুরের মধ্য দিয়ে কবিগুরু সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করার অবকাশ তৈরি করে দিয়েছেন। তার জন্য নতুনভাবে তার প্রকাশভঙ্গী বা সুর অথবা কথার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। অত্যধিক বেশী যন্ত্রানুষঙ্গের প্রযোগও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। গানের প্রধান বিষয়টি এতে ক্ষুণ্ন হয়। আসলে সৃষ্টিকর্তার যে নিজস্ব অভিব্যক্তি তাকে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন রঙে আরো বিভিন্ন করে তোলেন তিনি। বাংলা ভাষা ও গানের সুরের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই দায়িত্বই পালন করেছেন সুন্দরভাবে।
তথ্যসূত্র
১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খন্ড। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৯৫, ৪৪৮-৪৪
২। সত্যজিৎ -প্রতিভা ঘোষ বিজিত, পৃষ্ঠা ৪২