Dr. Moushumi Pal, Assistant Professor, Purnidevi Chowdhury Girls College, Bolpur, Birbhum
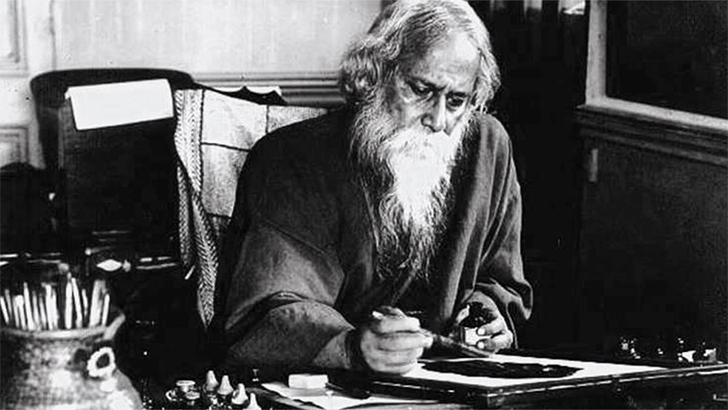
Abstract: The abstract highlights the extensive discussions and revisions regarding the intertwined nature of literature and music in the works of Rabindranath Tagore. The focus is on the significance of music in Tagore’s plays, stories, and poems, with an emphasis on the close relationship between literature and music, particularly in the context of theatre. The abstract suggests that understanding the songs in Tagore’s dramas reveals more than just a collection of musical pieces; it unveils songs depicting seasons, work, and thematic elements. Additionally, the abstract acknowledges the undeniable role of music in some of Tagore’s stories, indicating that certain songs may offer clues or hints about the underlying narrative. This study delves into the profound intersection of music and modernity in the literary works of Rabindranath Tagore, the revered polymath of Bengal. Tagore, a Nobel laureate poet, playwright, and philosopher, seamlessly integrated music into his creative expressions, transcending traditional boundaries and infusing his works with a distinctive rhythmic and melodic essence. This research examines how Tagore’s innovative use of music catalyzes the portrayal of modern themes in his plays, stories, and poems. By analyzing the intricate relationship between music and modernity in Tagore’s oeuvre, this study aims to unravel the nuanced layers of cultural, social, and existential significance embedded in his artistic creations. Through a comprehensive exploration of selected works, this research sheds light on Tagore’s unique approach to blending traditional musical elements with progressive ideas, thereby contributing to a deeper understanding of the symbiotic relationship between artistic expression, music, and the evolving landscape of modernity in Tagore’s literary legacy.
রবীন্দ্রনাথের নাটক, গল্প ও কবিতায় সঙ্গীতের প্রয়োগ ও আধুনিকতা
ড. মৌসুমী পাল, সহকারি অধ্যাপিকা, পূর্ণিদেবী চৌধুরী গার্লস কলেজ, বোলপুর, বীরভূম, E-mail – palkundu.mausumi9@gmail.com, Mobile No. : 9830353952
Abstract :
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক, গল্প এবং কবিতায় সঙ্গীতের সম্পর্ক নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা, পুনরালোচনার সম্মুখীন হয়েছি, যার মধ্যে বেশীরভাগই প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যমুখী এবং পরোক্ষভাবে সংগীত সংক্রান্ত। কয়েকটি ক্ষেত্রে নাট্যসংগীতের আলোচনায় অবশ্য সাহিত্য ও সংগীতের পরিমান ঘটেছে প্রায় সমান সমান। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকের গানগুলি খুব ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে সেগুলি শুধু গানের তালিকামাত্র নয়, তাতে স্থান পেয়েছে ঋতুবিষয়ক গান, কর্মসংগীত বিষয়ক গান, আবার কোথাও উদ্দেশ্যমূলক গান বা থিম সঙ্। তাছাড়া তাঁর কিছু কিছু গল্পে গানের ভূমিকার প্রাধান্য অস্বীকার করা যায়না। আবার কিছু কিছু গানের নেপথ্যে কোনো সম্ভাব্য গল্পের আভাসও মেলে।
রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মধ্যবর্তী সীমারেখাটি চিহ্নিত করা খুবই সমস্যামূলক। কারন রবীন্দ্রনাথের বেশীরভাগ গানই কবিতা। এর মধ্যে বেশকিছু কবিতাকেও রবীন্দ্রনাথ পরে সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে গানে রূপান্তরিত করেন। সাধারণভাবে এই সকল কবিতা – গানের সঙ্গে তাঁর গান-কবিতার কিছু পার্থক্য অনুভব করা যায়। কবিতা ও গানের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের ‘সহযোগিতা’ গ্রন্থে ‘সংগীত ও ভাব’, ‘সংগীত ও কবিতা’ প্রবন্ধগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সারাজীবন কবিতা ও গান একত্রে অনুশীলন করতে করতে রবীন্দ্রনাথ এই দুইয়ের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখেননি।
রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম গান – জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সরোজিনী’ নাটকে সংযোজিত চিতা প্রবেশের গানে (‘জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুন দ্বিগুন’) আসন্ন আত্মদানের পটভূমিতে যে তীব্র অভিশাপের রুদ্রবাণী ধ্বনিত হয়েছিল, তারই পরিণত রসঋদ্ধ রূপায়ন এই ‘দহন-সংগীত’।
রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের প্রয়োগ নিয়ে রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু আলোচনা আছে যেগুলিতে অধিকাংশই সাহিত্যের দিক থেকে আলোচনা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন – রমেন্দ্র নারায়ণ নাগের ‘রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা’ এইরূপ একটি গ্রন্থ১। তাছাড়া অরুণকুমার বসুর ‘বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত’ গ্রন্থে ‘নাটকের গান ও গানের নাটক’ নামক অধ্যায়ে২ এই সম্পর্কে যেমন গভীর তেমনি তথ্যপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়। অধ্যাপক বসুর ‘রবীন্দ্র বিচিন্তা’৩ গ্রন্থের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের ‘রাজানাটক ও রাজাতত্ত্ব’ প্রবন্ধেও এই জাতীয় সাংগীতিক, সাহিত্যিক বিচার দৃষ্টিগোচর হয়। শঙ্খ ঘোষের ‘নাটকে গান রবীন্দ্রনাথের নাটক’ এই বিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ন প্রবন্ধ৪। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়।
‘চোখের জলের লাগল জোয়ার’ অজয় রায় রচিত ‘শেষ বসন্তে রবীন্দ্রনাথ’ (প্রিন্টো বুকস্, ১৯৯৬) গ্রন্থের একটি অধ্যায়েও৫ রক্তকরবী নাটকে সংগীত প্রয়োগ সম্পর্কে একটি মননশীল আলোচনা স্থান পেয়েছে।
সুচিত্রা মিত্রের ‘রবীন্দ্রনাটকের গান’৬ শুধু রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানের তালিকা নয়, গানের শ্রেনীবিভাগও, তিনি নাটকে ব্যবহৃত রবীন্দ্রসংগীতগুলিকে ঋতুবিষয়ক গান, কর্মসংগীত,উদ্দেশ্যমূলক গান, থীম সঙ্ এইভাবে ভাগ করেছেন। জয়দেব রায়ের ‘রবীন্দ্রনাথের গানের পালা’য়৭ নাট্যগীতি ছাড়াও ঋতুনাট্য বা নটরাজ পালাগানের প্রসঙ্গও এসে গেছে। সেখানে গ্রীক নাটকের কোরাসের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সকল নাটকে একটি করে গানের দল রেখেছেন। সেই দলের অধিপতি স্বয়ং কবি, কখনও তাঁর নাম দাদাঠাকুর, কখনও বা ঠাকুরদা, কখনও বা ধনঞ্জয় বৈরাগী। ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ ও ‘কালমৃগয়া’ গীতিনাট্যে এই গানের দলে ছিল বনদেবীগণ, ‘মায়ার খেলা’য় মায়াকুমারীগণ, ঋতুনাট্যগুলিতে কোথাও কবিশেখর, কোথাও বা স্বয়ং নটরাজের দল।
কথাসাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ তাঁর ‘রবীন্দ্রনাট্যঃ গান দিয়ে দ্বার খোলানো’ প্রবন্ধে৮ সাহিত্যবুদ্ধিও নাট্যরসজ্ঞতার দুর্লভ এক দৃষ্টান্ত রক্ষা করেছেন। তাঁর মননে বোধে রসচেতনায় রবীন্দ্রনাথ যেন অন্তরঙ্গতম হয়ে উঠেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসিদ্ধি সংগীত সম্পর্কিত অভীপ্সার গভীর সূত্রগুলি সন্ধান করে সন্তোষকুমার ঘোষ লিখেছেন- ‘‘কোনো উৎসর্গপত্রই বলি, আর ব্রহ্মসংগীতই বলি, একটি গানে যাঁকেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা বলে থাকুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের স্থির ধ্রুবতারা কিন্তু ছিল সংগীতই। সেই সংগীত, নাটকের সহকারবৃক্ষকে লতার মতো জড়িয়ে উঠেছে। তাকে দুরন্ত তুরঙ্গম করে তুলতে পারে উধাও সুর, উদাত্ত ধ্বনি।’’
আবার এও লক্ষ্য করা যায়, যে ফাল্গুনী নাটকের মর্মবস্তু বিজন মন্দিরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে তখনই যখন একটি আর্ত অন্ধ বাউলের কন্ঠে ওই আকুল সংগীতটি গীত হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গান দিয়ে নাট্যবস্তুর অন্তরলোকের দ্বার খুলিয়েছেন। নিস্তব্ধ গিরিরাজকেও যিনি অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত রেখায় বিস্তারিত অভ্রভেদী সংগীতরূপে কল্পনা করেন, গান তাঁর সৃষ্টিলোকের চাবি হবে বইকি।
আর একজন কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে৯ রবীন্দ্রনাটকে সংগীত ব্যবহারের মর্মকথাকে উদ্ঘাটিত করেছেন। যেমন শুধু রক্তকরবীর ক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন –‘‘আরো ভালো উদাহরণ ‘রক্তকরবী’র মর্মগীতিটি। অর্থাৎ পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক। রক্তকরবীর সিদ্ধান্ত বাক্যটি কি? পুঁজিবাদী শোষণের বেড়াজাল তৈরী করে যে বিপুল শক্তিধর কর্মী মানুষটি তিলে তিলে আত্মনাশের মধ্য দিয়ে মরা ধনের শবসাধনা করছে, প্রেম আর সৌন্দর্যের তৃষ্ণায়, জীবনের আকুতিতে নিজের ধ্বজাদন্ডটি ভেঙে দিয়ে সে বেরিয়ে আসবে? সর্বসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে আবার নতুনভাবে আরম্ভ করবে জীবনসাধনা, দীক্ষা নিতে ছুটবে Socialism এর মন্ত্রে? আর এই সমাজতন্ত্রবাদের পালা গান শুরু হবে কারখানায়, নাগরিকতায় নয়, পল্লীপ্রকৃতির কোলে, কলতন্ত্র থেকে বেরিয়ে হল তন্ত্রে?’’ সাধারণভাবে এই কথাটির মনে হয় বটে, কিন্তু পৌষের গানটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে ‘রক্তকরবী’র পরম বক্তব্যটি এর চাইতে আরো কিছু বেশি। আসলে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে ধনতান্ত্রিক শোষণবাদের বিরুদ্ধে কন্ঠস্বর তুলে ধরলেও কোনো একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছেন না; যে কর্ষণজীবি সভ্যতার কথা তিনি বলছেন তাকে ‘এগ্রিকালচারল্ সিভিলাইজেশন’ মনে করলে ভুল করা হবে; বরং তা ‘ক্রিশ্চান মিলেনিয়ামে’র মতো যেদিন তরোয়াল ভেঙে লাঙল তৈরী হবে, খ্রীস্টের পুনরাবির্ভাবে ঐশ্বরিক ভক্তির ছত্রছায়ায় সমস্ত মানুষ একটি প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হবে। অর্থাৎ রক্তকরবীর শেষ কথায় কোনো বাস্তবসিদ্ধ রেখাবৃত্ত নেই, তার ভাবময়তায় বিকীর্ণ। ‘পৌষের গান’ কী বলছে?/ মাঠের বাঁশি শুনে আকাশ খুশি হ’ল-/ঘরেতে আজ কে রবে গো।/ খোলো দুয়ার খোলো’ ‘মাঠ’ এবং ‘আকাশ’ দুটো কথা আছে এর ভিতরে। এখানে মাঠ হল সামগ্রিক কর্ষণার প্রাণের অন্ন, আকাশ হল উর্ধ্বলোক, যেখান থেকে দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টিকিরণ মানুষের উপর বর্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ দেবলোকের করুণার চন্দ্রাতপতলে অহিংস নির্দ্বন্দ্ব মানুষ যে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, বিশেষ সামাজিক অবস্থা পার হয়ে সমস্ত প্যাটার্নকে অতিক্রম করে সেই ভাবক্ষেত্রেই ‘রক্তকরবী’র বিস্তার। ‘‘আর এই বক্তব্যটি হৃদয়ঙ্গম না হলে ‘রক্তকরবী’তে মাত্র সোশ্যালিষ্ট, রিভোলিউশনই পাওয়া যাবে। তাতে খুশি হওয়ার মতো নগদ বিদায় নিশ্চয় মিলবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপরে কোনোমতেই সুবিচার করা হবে না।’’ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে যে কথা ভিতর থেকে উঠে আসা মৌলিক চিন্তায় উদ্ভাসিত, সেইরূপ মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন পাওয়া যায় আলপনা রায়ের প্রবন্ধ দুটিতে১০, সুধীর চক্রবর্তী১১ ও অশ্রুকুমার সিকদারের প্রবন্ধে১২।
রবীন্দ্রনাথের ‘দুঃখের গান’ গ্রন্থে ‘নাটকের গান’ অধ্যায়ে১৩ নাটকের গানগুলিকে শ্রীমতী জয়ন্তী ভট্টাচার্য শান্তিদেব ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী এবং সাংগীতিক গুরুত্বের বিচারে দুই ভাগে বিভক্ত করলেও মূলত প্রথম ভাগ অর্থাৎ শান্তিদেব ঘোষ যেগুলিকে ‘গীতিনাট্য’ আখ্যা দিয়েছেন তারই আলোচনা করেছেন। শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে একমত হয়ে লেখিকা দ্বিতীয়ভাগের অন্তর্ভুক্ত ‘বসন্ত’ ‘শ্রাবণগাথা’, ‘ঋতুরঙ্গ’ এইগুলিকে তাঁর ‘গীতিনাট্য’ বলে মনে না হওয়ার জন্য তিনি এগুলিকে তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন নি।
১৮০৩ শকাব্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যগীতি ‘ভগ্নহৃদয়ে’র ‘সখী ভাবনা কাহারে বলে’ গানটিতে লেখিকার মতে “বিচ্ছেদ আছে, কিন্তু বিষণ্ণতা নেই । প্রকৃতির এই নিরাসক্ত লীলা কবিকে শিক্ষা দেয় মানবজীবনের চাওয়া-পাওয়ার খেলায় অবিচলিত থাকতে—বৃহত্তর জীবনবোধের পটভূমিতে স্থাপিত করে আবিষ্কার করতে খণ্ড খণ্ড সুখ দুঃখের সামগ্রিক তাৎপর্যকে।” (পৃ. ১০৪ )
এরপর ‘মায়ার খেলা’নৃত্যনাট্যের ‘আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই’ গানে কবির মনে জেগেছে প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা। ‘রাজা ও রাণী’ নাটকে মিলনের প্রত্যাশার মধ্যে ঘটেছে বেদনার ছায়া পাত যা কিনা পরবর্তী ‘ঐ বুঝি বাঁশি বাজে’ গানে সুখের মাধুর্যের বদলে পরিণতি লাভ করেছে তীব্র উৎকণ্ঠার হাহাকারে এবং পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে চিরবিদায়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে ‘আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি’ গানে। ১৩৩৬ সালে লাহোর জেলে যতীন দাসের অনশনের ফলে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গানটি লিখেছিলেন সেটি পরে ‘তপতী’ নাটকের অন্তর্ভুক্ত হয়। গানটি হল ‘সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ’। ‘তপতী’ নাটকের আরও গানগুলি হল ‘আমি সকল নিয়ে বসে আছি’, ‘আমি তোমার প্রেমে’, ‘এ অন্ধকার ডুবাও’, ‘দিনের পরে দিন যে গেল’। এই রকম আরও কিছু কিছু নাটকের গানের উল্লেখ করা যায়। যেমন—‘বিসর্জন’ নাটকের ‘আমারে কে নিবি ভাই’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকের ‘আজ তোমারে দেখতে এলেম’, ‘চিরকুমার সভা’র না বলে যায় পাছে সে’, ‘তোমায় চেয়ে আছি বসে’ বা ‘জ্বলে নি আলো অন্ধকারে’,‘শোধবোধ’নাটকের ‘বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা’, ‘উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল’, ‘শেষরক্ষা’ নাটকের ‘হায় রে ওরে যায় না কি জানা’, ‘যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে’, ‘কাছে যবে ছিল’, ‘মুখপানে চেয়ে দেখি, ‘গৃহপ্রবেশ’নাটকের ‘খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি’, ‘রক্তকরবী’র ‘তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে’,‘তোমায় গান শোনাব’, ‘ভালোবাসি, ভালোবাসি’, ‘অচলায়তনে’র পঞ্চক বা ‘ফাল্গুনী’ নাটকের কবি শেখরের মুখের গান ‘পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে’।
এছাড়া কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্র গল্পে গান’ নামে একটি প্রবন্ধে১৪ কিছু কিছু গল্পে গানের সামান্য উল্লেখ করেছেন। অন্যদিক থেকে সৌমেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ‘ভ্রষ্টলগ্নের গান’১৫ নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিছু গানের নেপথ্যে কোনো সম্ভাব্য গল্পের আভাস দিয়েছেন।
আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের মাঝখানের সীমান্তরেখাটি যে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য যে ব্যাপারে অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের গান’১৬ গ্রন্থে কিছু আলোকপাত করেছেন। যেমন – ‘‘রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব গান সুরের ফ্রেমে ভেবে নিয়ে লিখেছিলেন কিনা। না লিখে থাকলে কোন্ কোন্ গান তিনি সুরের ধারায় মিলিয়ে ছন্দ ও ভাষা দিয়েছিলেন?’’
এ ব্যাপারে অবশ্য কোনো প্রামান্য তথ্য মিলবে না রবীন্দ্রনাথের উক্তি ছাড়া। এক্ষেত্রে গান-কবিতা রচনার সময় কবিমনে সুরের সহযোগিতা কিছু মেনে নিতে হবে। আর গ্রন্থনামে (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি) এবং তাঁর আগে এরূপ রচনার শীর্ষে (‘কল্পনায়’ ও ‘খেয়ায়’) আর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আবার কোথাও কোথাও রাগ-তাল নির্দেশ থাকলে তো কথাই নেই। এটাও মেনে নেওয়া প্রাসঙ্গিক যে সব গান-কবিতায় সুরের সহযোগিতা সমান পরিমানে নয়, যেখানে রচনাটি একটু দীর্ঘ সেখানে সুরের সহযোগিতা কম বলে মনে হয়। গান-কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল এক-মিল, অন্ততপক্ষে প্রথম ও শেষ পদে। ব্যতিক্রমও আছে।
কবিতা ও গানের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে প্রথম আলোচনা রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনে ‘সহযোগিতা’ নামক গ্রন্থে ‘সংগীত ও কবিতা’, ‘সংগীত ও ভাব’ প্রবন্ধগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটেছে। সারাজীবন কবিতা ও গান অনুশীলন করতে করতে রবীন্দ্রনাথ এই দুইয়ের মধ্যে কোনো বেড়া রাখেননি। কবিতা ও সংগীতের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষন ও রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন অধ্যাপক অরুণ কুমার বসু তাঁর ‘বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে১৭। তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে ‘যুগলমিলন স্রোতে’ শিরোনামে কবির বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত গান ও সুরারোপিত কবিতাগুলির যে আলোচনা আছে অনুরূপ বিষয়ে তাঁর পূর্বে আর কোনো আলোচনা আমাদের চোখে পড়েনি। তবে পরবর্তীকালে এই বিষয়ে কেউ কেউ আরো আলোচনা করেছেন। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর ‘রবীন্দ্রসংগীত’ গ্রন্থের ‘কাব্যগীতি’ নামক অধ্যায়ে১৮ এই বিষয়ে একটা প্রাথমিক খসড়া করেছিলেন। তাছাড়া সুধীর চক্রবর্তী ‘কবিতা আর গানের আকাশঃরবীন্দ্রনাথ’ নামে তাঁর ‘গানের লীলার সেই কিনারে’ গ্রন্থে (১৩৯২)১৯, শঙ্খ ঘোষের ‘এ আমির আবরন’ (১৯৮০) গ্রন্থের ‘ধরেছি ছন্দবন্ধনে’ প্রবন্ধটিতেও২০ এই বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে। এই বিষয়ে অবশ্য বিচ্ছিন্ন কিছু প্রবন্ধও আমাদের চোখে পড়েছে। সেগুলির মধ্যে ‘বাণী ও বীণা’ প্রবোধচন্দ্র সেনের এই দিক নির্ণায়ক প্রবন্ধটি২১ মূলত রবীন্দ্রনাথের গানের ছন্দে কাব্যছন্দের বিশিষ্টতা ও পদ্ধতি নিরূপণ করা।
‘কড়ি ও কোমল:শতবর্ষের গান’ হর্ষ দত্তের এই প্রবন্ধটিতে২২ ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে কড়ি ও কোমলের ‘হেলাফেলা সারাবেলা’, ‘আজি শরততপনে প্রভাত স্বপনে’ গান দুটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন – ‘‘এ যে গোপন তন্ত্রীতে বেজে ওঠা দুঃখী প্রাণের গভীর দীর্ঘশ্বাস। স্বতঃই মনে হয়, এদুটি গানেরও রচনা উপলক্ষ্য কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু। এদের বাণী সামান্যত স্পর্শ করে আছে শরৎ ঋতুর সোনালি দিনের বসনাঞ্চল। কিন্তু সমগ্র অবয়বে এ গান ধরে রেখেছে ব্যথার পূজার অর্ঘ্য।’ (পৃঃ ৪০) যদিও এ প্রবন্ধ প্রকাশের বহু পূর্বে অধ্যাপক অরুণ কুমার বসুর ‘বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত’ গ্রন্থে আমরা এই মন্তব্য পেয়েছিলাম।
ঋষিণ মিত্র আধুনিক কবিতায় সুরারোপ করে খ্যাতিলাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনেক কবিতার ওপর সুরারোপ করে গানে পরিণত করেছেন। শ্রীমিত্র তাঁর ‘আধুনিক কবিতার গীতিরূপ ও রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকটি দিক’ প্রবন্ধে২৩ রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাকে গানে রূপান্তরিকরণের আদর্শকে মানদন্ড করে তাঁর আধুনিক কবিতার ওপরে সুর দেওয়ার যোগ্যতা ও পদ্ধতিকে বুঝে নিতে চেয়েছেন।
রবীন্দ্রসংগীতের দুটি দিক তার সুর ও বাণীর ক্ষেত্র- রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক আলোচনায় প্রায় সমান গুরুত্ব পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪৬) রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গানগুলিকে পূজা, স্বদেশ, আনুষ্ঠানিক, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র প্রভৃতি পর্যায়ে নির্দেশ করে বলেছিলেন, এই ভাবের অনুষঙ্গে সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠক গীতিকাব্যরূপে গানগুলির আস্বাদন করতে পারবেন।
উল্লেখপঞ্জী
১) রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা – রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ, ডি.এম.লাইব্রেরি, ফাল্গুন, ১৩৮৮
২) বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত- অরুণ কুমার বসু, দে’জ, আগষ্ট, ১৯৯৪ (২য় সং)
৩) রবীন্দ্রবিচিন্তা – অরুণকুমার বসু, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, মহালয়া, ১৩৫৭
৪) রবীন্দ্রনাথ মনন ও শিল্প – সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, নাটকে গান রবীন্দ্রনাথের নাটক – শঙ্খ ঘোষ, প্রকাশক?
৫) শেষ বসন্তে রবীন্দ্রনাথ – অজয় রায়, প্রিন্টো বুক্স, ১৯৯৬।
৬) রবীন্দ্রনাটকের গান – সুচিত্রা মিত্র, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, বর্ষ-২, সংখ্যা ১, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৮
৭) রবীন্দ্রনাথের গানের পালা – জয়দেব রায়, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, বর্ষ-২, সংখ্যা-১, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৮।
৮) রবীন্দ্রনাট্যঃ গান দিয়ে দ্বার খোলানো- সন্তোষ কুমার ঘোষ, চতুরঙ্গ, বর্ষ ৪৫, সংখ্যা – ২, জুন ১৯৮৪
৯) রবীন্দ্রনাট্যে গানের ভূমিকা – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গীতবিতান জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ (১ম) ১৯৬১
১০) রবীন্দ্রনাটকে গানের সুর – রক্তকরবীর গান- আলাপ থেকে বিস্তার – আলপনা রায়, প্যাপিরাস, মে ১৯৯২।
১১) গানের লীলার সেই কিনারে – সুধীর চক্রবর্তী, বাংলা নাটকের গান, রবীন্দ্রনাটকের গান, অরুণা, নববর্ষ, ১৩৯২
১২) রবীন্দ্রনাটকের গান- অশ্রুকুমার সিকদার,
১৩) রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান- জয়ন্তী ভট্টাচার্য, করুণা প্রকাশনী, ১৩৯২
১৪) রবীন্দ্রগল্পে গান- কণিকা বন্দোপাধ্যায়, গল্পগুচ্ছ (বিশেষ রবীন্দ্র সংকলন), বর্ষ-৬, সংখ্যা – ২, গ্রীষ্ম ১৩৯০।
১৫) ভ্রষ্টলগ্নের গান – সোমেন্দ্রনাথ বসু, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯০ সালে (জোড়াসাঁকোতে অনুষ্ঠিত বৈতানিকের একটি অনুষ্ঠান থেকে গৃহীত)।
১৬) রবীন্দ্রনাথের গান- সুকুমার সেন, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৮মে, ১৯৯৮
১৭) বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত- অরুণকুমার বসু, দে’জ, আগষ্ট, ১৯৯৪ (২য় সং)
১৮) রবীন্দ্রসংগীত – শান্তিদেব ঘোষ, বিশ্বভারতী, ৭ই পৌষ, ১৩৪৯
১৯) গানের লীলার সেই কিনারে- সুধীর চক্রবর্তী, কবিতা আর গানের আকাশঃ রবীন্দ্রনাথ, অরুণা, নববর্ষ, ১৩৯২
২০) এ আমির আবরণ – শঙ্খ ঘোষ, ধরেছি ছন্দবন্ধনে, প্যাপিরাস, ১৯৮০
২১) বাণী ও বীণা – প্রবোধচন্দ্র সেন, গীতবিতান, রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী সংকলন, অক্টোবর, ১৯৬১
২২) কড়ি ও কোমল – শতবর্ষের গান – হর্ষ দত্ত, দেশ সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৯৩
২৩) আধুনিক কবিতার গীতিরূপ ও রবীন্দ্রসংগীতের কয়েকটি দিক- ঋষিণ মিত্র, অতিথি, বর্ষ-১২, ১৩৮৭।