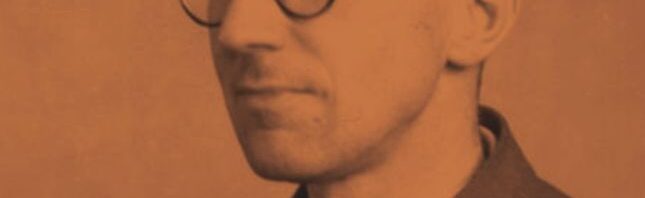Bertolt Brecht in Modern Bengali Theatre
Sayanti Ghatak, Ph. D. Scholar, Rabindra Bharati University
Abstract:
This study delves into the introduction of the proscenium stage in Bengali theater, attributing its debut to Gerasim Stepenevich Lebedev on November 27, 1795. Lebedev, a foreign literature enthusiast, not only marked this historical moment by presenting the first proscenium play in Bengal but also translated a foreign play, “The Destroy,” into Bengali as “Kalpanik Sambandal.” Consequently, foreign translated dramas, particularly those of Bertolt Brecht, significantly influenced Bengali theater. Brecht’s epic theater, known for its socio-political commentary, found resonance in Bengal. Despite being born in 1898, Brecht’s impact on global theater, shaped by two world wars, fascinated Bengali playwrights and directors. Notably, Ajitesh Bandyopadhyay, a key figure in Bengali theater, highlighted Brecht’s innovative staging techniques, drawing parallels between Brecht’s Caucasian Chalk Circle and traditional Sanskrit drama. The study examines how Brecht’s plays, with their distinctive blend of music, ballads, and stylized performances, were integrated into Bengali theater. Ajitesh Banerjee, a prominent playwright-actor, acknowledges the influence of Brecht’s plays in his drama presentations, emphasizing the importance of conveying messages to the audience. Additionally, Badal Sarkar, a pioneer in the third style of Bengali theater, finds Brecht’s plays instrumental in highlighting the essence of dramatic presentations and creating awareness among the audience. Furthermore, Utpal Dutta, another influential director in the theater world, emphasizes understanding Brecht’s political struggle to grasp the depth of his dramaturgy. Brecht’s rebellion against old theatrical norms and his advocacy for a new theater that challenges established ideas and habits are explored as essential elements in the integration of Brechtian style into Bengali theater. In conclusion, the study illuminates the intersection of Brechtian theatrical techniques with the rich cultural heritage of Bengali theater. The incorporation of foreign elements into the traditional Bengali dramatic landscape reflects the dynamic nature of theatrical evolution and the enduring relevance of Brecht’s ideas in the context of Bengali theater.
আধুনিক বাংলা থিয়েটারে ব্রের্টোল ব্রেখ্ট্, সায়ন্তী ঘটক, পিএইচ. ডি. স্কলার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা থিয়েটারে মঞ্চনাটক বা প্রসেনিয়াম এর আবির্ভাব হয়েছিল একজন বিদেশি সাহিত্যপ্রেমী মানুষের হাত ধরে। 1795 সালে 27 শে নভেম্বর কলকাতার ডোম তলায় একটি বাড়ির উঠোন ভাড়া করে গেরাসিম স্টিপেনভিচ লেবেদেফ বাংলার বুকে প্রথম প্রসেনিয়াম বা মঞ্চনাটকের উপস্থাপনা করেন তাও “দি ডেস্ট্রয়”নামে একটি বিদেশী নাটকের বাংলা অনুবাদ “কাল্পনিক সংবদল” নামে উপস্থাপনা করেন। যেহেতু প্রসেনিয়াম উপস্থাপনার বিষয়টি সম্পূর্ণ বিদেশিদের হাত ধরে বাংলায় প্রবেশ করেছে তাই পরবর্তীতে বাংলা থিয়েটারে প্রসেনিয়াম বা মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে বিদেশি নাট্যকারদের(অনুবাদ) নাটক বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। বিদেশি অনুবাদ নাটক গুলির মধ্যে নাট্যকার ব্রেখ্ট্ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয়, তার নাটককে এপিক থিয়েটার বলা হয় যা সর্বকালীন প্রাসঙ্গিক কিন্তু বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে তিনি শুধু একজন নাট্যকার নন বরং তার নাট্য নির্দেশনার ধরনের( অ্যালিনেশন) জন্য তিনি বাংলা থিয়েটারে ভীষণ ভাবে চর্চিত এবং জনপ্রিয়। ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী বাংলা ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে অবস্থিত তাই ভরতের নাট্যশাস্ত্র মতে কনটেন্টের ভিত্তিতে ভারতি ও কৌশিক বৃত্তির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ সংলাপ এবং নৃত্যগীত এই দুয়ের প্রভাব পূর্ব ভারতের অঞ্চল গুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অপরদিকে বাংলার নিজস্ব নাট্য রস বলতে বোঝায় বাংলার লোকনাট্য এবং যাত্রা। এগুলি মূলত বাংলার নাট্যচর্চার নিজস্ব উপাদান। বাংলা এই নিজস্ব ধরন বর্তমানে যেভাবে ব্রেখ্ট্ সাহেবের নাটক ও তার নাট্য ধরনকে একাত্ম করে নিয়েছে সেখানেই আমার কৌতুহল। ব্রেখ্ট্ এর জন্ম সাল 1898 এবং সেই সালেই মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ রাশিয়ায় তখন ন্যাচারালিস্টিক, রিয়েলিস্টিক অভিনয়ের চূড়ান্ত চর্চা চলছে। ব্রেখ্ট্ তার জীবন কালে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে এবং সেই প্রভাব সরাসরি তার নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা নাট্যজগতের দিকপাল অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় তিনি তার লেখায় বলছেন (“অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ সংগ্রহ” প্রকাশক -তন্দ্রা চক্রবর্তী ,নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট)’ ব্রেখ্ট্ ককেশিয়ান চক সার্কেলে তিনি বলেছিলেন এশিয়ান চক সার্কেল বহুদিন অবধি কথাটা আমার মনে গেঁথে ছিল। একবারের প্রযোজনায় মঞ্চে পশ্চাদপটে একটা চাকার ছায়া ফেলেছিলেন। চাকাটা ঘুরছিল, ক্রমাগত ঘোড়ার একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ আগাগোড়া চলছিল নাটকে ব্রেখ্ট্ এগিয়ে এসে বললেন আপনারা পাঁচ মিনিট মন দিন বাকি আড়াই ঘন্টা নাটক টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। সত্যি সত্যি তাই,ওই চাকা ঘোড়ার ছায়া অনবরত ক্যাঁচকোঁচ শব্দ দর্শকদের সম্মোহিত করে রেখেছিল। সর্বোপরি প্রত্যেক অভিনেতা স্টাইলাইজড অভিনয় করেছিলেন প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ভঙ্গি যেমন চাষী হাত কচলায় তো মিনিটে মিনিটে তাই করে, রাজা গোঁফে তা দেয় তো মিনিটে মিনিটে তাই করেন এইরকম আর কি। এবং প্রত্যেক অভিনেতা কেউ সুরে অথবা সুর হীনতায় সংলাপ বলে চলে, যখন নাটক চড়ায় ওঠে তখনই একজন এসে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে যায় সেই সময়টা দর্শকের চোখের সামনে মঞ্চসজ্জা সাজান হতে থাকে তবু দর্শক সম্মোহিত হয়ে চুপচাপ বসে থাকে। আমি অবশ্য ভালো বুঝিনি কিন্তু ব্যাপারটার নতুনত্বে খানিকটা ভাবলুম ব্রেখ্ট্ গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য তার মাঝামাঝি কিছু করতেন। এরপর যা শুনলাম ব্রেখ্ট্ তার নাটকের গঠনশৈলী নিয়েছেন সংস্কৃত নাটক থেকে। জার্মানিতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা আছে ব্রেখ্ট্ সংস্কৃত নাটকের মতো করেই তার নাটকগুলোর সাজিয়েছেন। কিন্তুুু ভাবলুম নাটকের মাঝখানে গান ঢোকানোর পরিকল্পনা তো ব্রেখ্ট্ সংস্কৃত নাটক থেকে পেতে পারেন না সংস্কৃত নাটক গুলিতে মাঝে মাঝে কবিতা আছে কিন্তুুু গান কদাচ নয়। বরং আছে বাংলার যাত্রায়, আর যাত্রা তো সংস্কৃত থেকে দূর লোকায়ত।বুঝতে মুশকিল হলো আরো এর জন্যই যে তিনি গান ব্যবহার করেছিলেন দর্শকদের নাটকের নাটকীয়তা থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রেখে তাদের বিশ্লেষণ করবার সময় দেবেন বলে। তিনি চাইতেন তার দর্শক যেন কখনোই না ভোলেন তারা নাটক দেখতে এসেছেন।’ নাট্যকার অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও ব্রেখ্ট্ এর নাটকে বাংলার ধরন খুঁজে ছিলেন।
বাংলা নাট্য জগতের তৃতীয় ধারার প্রবর্তক বাদল সরকার, তিনি নিজের নাটক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বলেছেন ‘আমি যে নাট্য উপস্থাপনায় বিশ্বাসী তাতে ব্রেখ্ট্ এর নাটক ভীষণভাবে আমার সাহায্য করে কারণ ব্রেখ্ট্ এর নাটকে তার নাট্য উপস্থাপনার রস লুকিয়ে থাকে।অ্যানিলেশন বা ভ্রেরফ্রেমডু্্ যাই বলি না কেন এর মূল কাজ দর্শককে নাটকের বক্তব্যের প্রতি সচেতন করা, যার ফলে নাট্যকার বা নির্দেশক যে বার্তা পৌঁছতে চাইছেন তা দর্শক মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে, যা দর্শককে ভাবতে বাধ্য করবে এবং নাট্যজগতের আরেক দিকপাল উৎপল দত্ত মহাশয় তিনি বলেছিলেন ‘ব্রেখ্ট্ কে জানতে হলে তার নাট্য রসের গভীরতা বুঝতে হলে তার রাজনৈতিক লড়াইকে জানতে হবে,বুঝতে হব, কারণ ব্রেখ্ট্ তার এপিক থিয়েটার এর নাট্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে পুরনো চিন্তার দাসত্ব করে নতুন থিয়েটার গড়ে উঠতে পারে না ,তাই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন পুরনো নাট্যচিন্তা এবং অভিনেতা, মঞ্চ কুশলী ও দর্শকের সমস্ত পুরনো অভ্যাসের বিরুদ্ধে’।
ব্রেখ্ট্ যে মার্কসবাদকে তার থিয়েটারের মূল প্রাণ শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন সেই মার্কসবাদী শিল্প চিন্তার মতে প্রতিটি শিল্প সৃষ্টি ও দার্শনিক তত্ত্ব হলো তার নিজস্ব যুগের চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ কিন্তু প্রকৃত মাক্সবাদী সেখানেই থেমে থাকে না। 1952 খ্রিস্টাব্দে ব্রেখ্ট্ বলেছিলেন ‘শিল্পকে বিশেষভাবে থিয়েটারেকে অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে কিন্তু সেই থিয়েটার এর মূল লক্ষ্য হবে এন্টারটেইনমেন্ট বা প্রমোদ’ এই কথা বলেই তিনি শতাব্দী-প্রাচীন জার্মান থিয়েটারের মূলস্রোতে নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করে তোলেন। ব্রেখ্ট্ এর মতে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি যথাযথ মঞ্চে হাজির করলে তার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব, কারণ অভ্যাসবশত তা আমরা অনিবার্য বলে মেনে নিই। তাই প্রযোজনার ক্ষেত্রে এপিক থিয়েটার এ নানা ভঙ্গিগত চমক সৃষ্টি করতে হয় যাকে বলা হয়”erstaumen” । এপিক থিয়েটার এর ভঙ্গিতে নাটক প্রযোজনার ব্যাপারে ব্রেখ্ট্ সব সময় তার সহযোগীদের যে মূল বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলতেন তা হল গল্প করার রূপরীতি। তিনি নাটকে সুষ্ঠুভাবে ঘটনার ধারাবাহিকতা তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন। নাটকের চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যতনা বেশি সচেতন, তারচয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন ঘটনার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ক্রমবিকাশে, যেহেতু তার নাটক মূলত মেহনতী মানুষের জন্য তাই তিনি উপকথা, রূপকথা, প্যারাবল এই সকল এপিক এর সরল ভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট হন। থিয়েটারের কাছে ব্রেখ্ট্ এর ভাষায়, সর্বপ্রকার সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চেহারা একমাত্র এপিক ভঙ্গিতেই তাকে বিধৃত করা সম্ভব। বর্তমান যুগের মানুষের কথা বলার জন্য ব্রেখ্ট্ এপিক থিয়েটারে মহাকাব্যের রীতিকে প্রয়োগ করেছেন। মহাকাব্য দূরত্ব বজায় রাখে ফলে তা দৈনন্দিন জীবনের ঘটনায় আবদ্ধ নয়, মহাকাব্যের ঐতিহ্যই তাই। কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্রেখ্ট্ এর রাজনীতি ও নাট্যতত্ত্ব বাতিল করে তার থিয়েটারের ভঙ্গি গত বৈশিষ্ট্য গুলি নিয়ে বহুবিধ আলোচনা হয়।
বাংলা নাটক জগতের প্রবীণ নাট্য শিক্ষক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত মহাশয় তিনি বলছেন ‘ব্রেখ্ট্ কে অ্যালিনেশন,ভ্রেরফ্রেমডু্্ এই সমস্ত বড় বড় কথা দিয়ে ভাবলে চলবে না। কারণ তিনি যে পরিকাঠামোতে থিয়েটার করেছেন সেই পরিকাঠামো আজও আমাদের বাংলায় তৈরি হয়নি কিন্তু ব্রেখ্ট্ কে আমরা নিজেদের মতো করে বাংলার ধরনের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপনা করে চলেছি’। নাট্য শিক্ষক অরুণ মুখোপাধ্যায় তিনি বলছেন ‘ব্রেখ্ট্ এর নাটকের ধরন বাংলার নিজস্ব আঙ্গিকের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে যেহেতু ব্রেখ্ট্ পাশ্চাত্যের বহুদেশের নাট্যরূপ ও স্থাপনার ধরন-ধারণ নিজের নাটকে ব্যবহার করেছেন তাই এই মিল খুঁজে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক’।
নাট্য নির্দেশক আশিষ দাস তিনি বলেছেন ‘ব্রেখ্ট্ এর নাটক তিনি বাংলাতেই পড়েছেন ইংরেজিতে বা জার্মানি ভাষায় পড়েননি তাই বাংলায় সেই নাটকটি( ককেশিয়ান চক সার্কেল) পড়ার পর সেই নাটকের ধরন, গঠন এবং উপস্থাপন শৈলী তার অনেকটাই বাংলা ‘অষ্টক’ লোক আঙ্গিকের মতোই লেগেছে’। আবার নবীন নাট্যকার শুভঙ্কর দাসশর্মা তার মতে ‘ব্রেখ্ট্ এর নাটক এবং তার নাট্যশৈলী বাংলা থিয়েটারে নাট্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক নতুন স্টাইলাইজ ধারার প্রবর্তন ঘটিয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে ব্রেখ্ট্ এর অ্যানিলেশন নয় অথচ তার ধরনকে সবদিক থেকেই অনুসরণ করছে। কিন্তু সেই নাটক দর্শক উপভোগ করার পর সেখানে তারা আলাদা করে ব্রেখ্ট্ এর ধরন খোঁজার চেষ্টাও করেন না বা খুঁজেও পান না তাই কোথাও গিয়ে মনে হয় বাংলার নাটকের ধরন ও ধারার সাথে বর্তমান সময়ে ব্রেখ্ট্ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।’এই মিল পাওয়া এবং না পাওয়ার মাঝে একজন বিদেশি নাট্যকারের হাত ধরে বাংলার নাটক এবং বাংলার থিয়েটার বিবর্তিত হয়ে চলেছে, যেই ধারা আজও বহমান।
তথ্য সূত্র
1.দত্ত, উৎপল। ‘স্তানিস্লাভস্কি থেকে ব্রেখ্ট্,’ নাট্য ভাবনা, কলকাতা :1942
2. চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ। ‘ব্রের্টোল্ট ব্রেখ্ট্ ও তার থিয়েটার’, নাট্যকলা, 7. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা:2007
3. বন্দোপাধ্যায়, সত্য। ‘ব্রের্টোল্ট ব্রেখ্ট্ ও আধুনিক থিয়েটার’,নাট্য আকাডেমী পত্রিকা 3, কলকাতা:1993
4. ‘অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ সংগ্রহ’ নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, প্রকাশক-তন্দ্রা চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ:1991
5. ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ “ব্রের্টোল্ট ব্রেখ্ট্’, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রচ্ছদ-রথীন চক্রবর্তী,কলকাতা:14